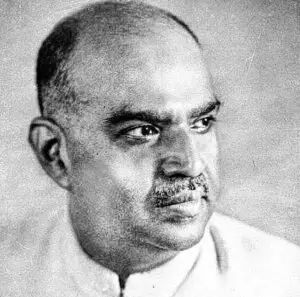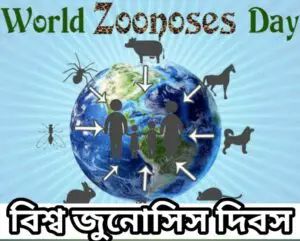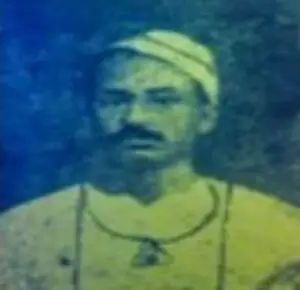নগেন্দ্রনাথ বসু র জন্ম 6 জুলাই 1866 সাল। তিনি ছিলেন বাংলা এনসাইক্লোপিডিয়ার কম্পাইলার, বাংলার প্রথম বিশ্বকোষ, এবং হিন্দি এনসাইক্লোপিডিয়ার লেখক, হিন্দিতে প্রথম বিশ্বকোষের লেখক, সেইসাথে একজন প্রত্নতাত্ত্বিক এবং ইতিহাসবিদ। রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় এবং ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় বাংলা বিশ্বকোষের প্রথম খণ্ড সম্পাদনা করেন।
যাইহোক, পরবর্তী 22টি পর্ব নগেন্দ্রনাথ বসু নিজেই প্রকাশ করেছিলেন, যার জন্য 1911 সাল পর্যন্ত 27 বছর সময় লেগেছিল। বাংলা বিশ্বকোষের 24টি পর্ব 1916 এবং 1931 সালে প্রকাশিত হয়েছিল। নগেন্দ্রনাথ বসু তার কর্মজীবনের প্রথম দিকে কবিতা ও উপন্যাস লেখা শুরু করেন এবং দুটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তিনি প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা করার জন্য ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি বাংলা, সংস্কৃত ও ওড়িয়া ভাষার প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন এবং পাথর ও তাম্রপাতে অঙ্কন করেন। তাঁর পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের ফলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বাংলা বিভাগ চালু করার অনুমতি পায়।
রচনা—
দুটি বিশাল বিশ্বকোষ এবং বাংলা ক্লাসিক ছাড়াও, তিনি ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের উপর বেশ কিছু রচনা প্রকাশ করেছেন।
কায়স্থের বর্ণপরিচয়, মাল্টিভলিউম বাঙালি জাতীর ইতিহাস,আধুনিক বৌদ্ধধর্ম এবং উড়িষ্যার অনুসারী এবং, কামরূপের সামাজিক ইতিহাস, ময়ূরভঞ্জ প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ।
সম্মাননা—
নগেন্দ্রনাথ বসুর কাজকে সম্মান জানিয়ে কলকাতা পৌরসংস্থা “বিশ্বকোষ” লেন নামে একটি রাস্তার নাম করণ করেছে। তিনি “প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব” শিরোনামে ভূষিত হন।
মৃত্যু—-
11 অক্টোবর 1938 সালে তিনি প্রয়াত হন।
।।তথ্য : সংগৃহীত উইকিপিডিয়া ও বিভিন্ন ওয়েবসাইট।।