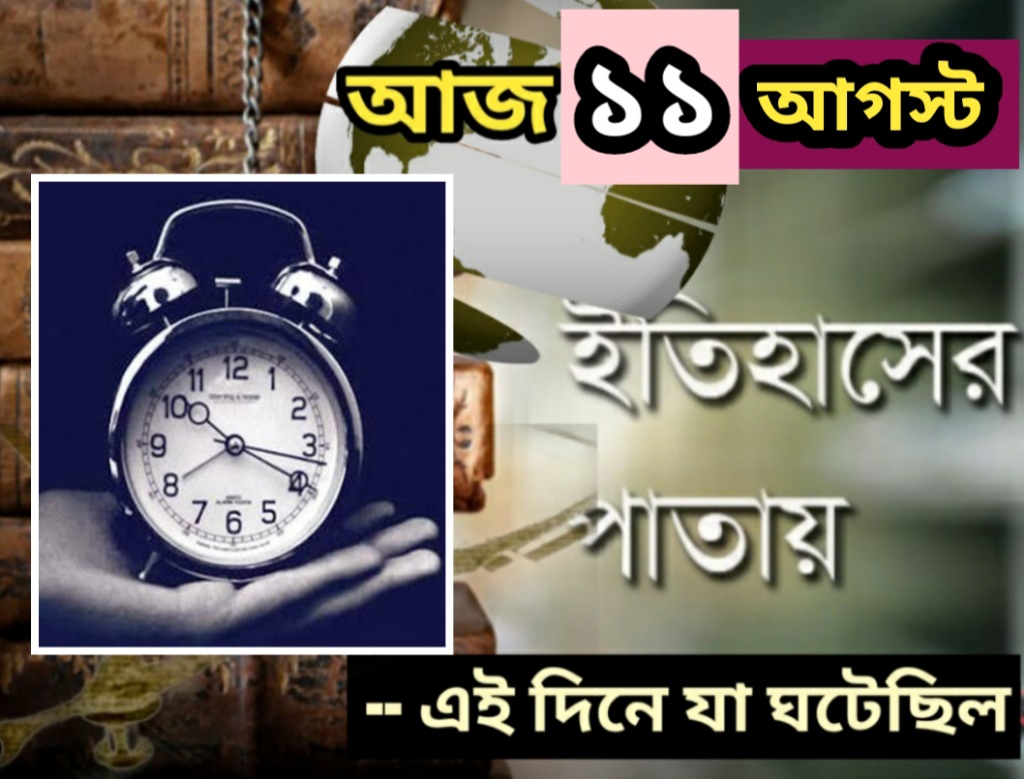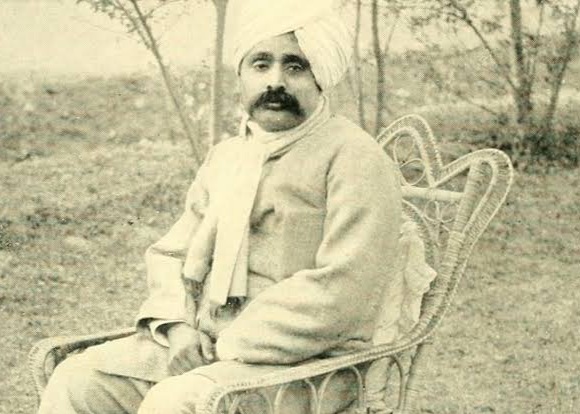আজ ১৬ আগস্ট। ইতিহাস ঘেটে দেখা যায় বছরের প্রতিটি দিনে ঘটেছে অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আসুন আজকের দিনে ঘটে যাওয়া উল্লেখযোগ্য কিছু বিষয় একনজরে দেখে নিই। ইতিহাসের আজকের এই দিনে কী কী ঘটেছিল, কে কে জন্ম নিয়েছিলেন ও মৃত্যুবরণ করেছিলেন——-
আজ যাদের জন্মদিন—-
১৯০৪ – ওয়েন্ডেল মেরেডিথ স্ট্যানলি, মার্কিন রসায়নবিদ এবং ভাইরাসবিদ।
১৯১৩ – মেনাখেম বেগিন, ইসরায়েলের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ।
১৯৩০ – ইংরেজ কবি ট্রেড হিউজ।
১৯৪৬ – মাসউদ বারজানি, ইরাকে স্বায়ত্তশাসিত কুর্দিশ সরকারের রাষ্ট্রপতি এবং কুর্দিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রধান নেতা।
১৯৫০ – জেফ থমসন, সাবেক ও বিখ্যাত অস্ট্রেলীয় ক্রিকেট তারকা।
১৯৫৪ – জেমস ক্যামেরন, একাডেমি পুরস্কার বিজয়ী কানাডীয় চলচ্চিত্র পরিচালক, প্রযোজক ও চিত্রনাট্য লেখক।
১৯৫৮ – ম্যাডোনা, আমেরিকান গায়ক-গীতিকার, প্রযোজক, অভিনেত্রী, এবং পরিচালক।
১৯৬০ – টিমোথি হাটন, আমেরিকান অভিনেতা, প্রযোজক ও পরিচালক।
১৯৬২ – স্টিভ কারেল, আমেরিকান অভিনেতা, পরিচালক, প্রযোজক এবং চিত্রনাট্যকার।
১৯৬২ – আইয়ুব বাচ্চু, বাংলাদেশী সঙ্গীত শিল্পী।
১৯৬৬ – তারানা হালিম, বাংলাদেশী টেলিভিশন অভিনেত্রী, নাট্য পরিচালক, লেখক, আইনজীবী এবং সমাজকর্মী।
১৯৬৮ – অরবিন্দ কেজরীওয়াল, ভারতীয় রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মী, ভারতীয় রাজস্ব সেবার প্রাক্তন কর্মকর্তা, দিল্লির সপ্তম মুখ্যমন্ত্রী ও আম আদমি পার্টির প্রতিষ্ঠাতা।
১৯৭০ – সাইফ আলি খান, ভারতীয় অভিনেতা এবং প্রযোজক।
১৯৭০ – মনীষা কৈরালা, ভারতীয় অভিনেত্রী।
১৯৭৪ – শিবনারায়ণ চন্দরপল, সাবেক ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ক্রিকেটার।
১৯৮০ – শাহিদা বেগম, কক্সবাজারের শ্রেষ্ঠ সহকারী প্রাথমিক শিক্ষিকা।
১৯৯৭ – গ্রেসন চ্যান্স, আমেরিকান সংগীতশিল্পী।
১৮২১ – আর্থার কেলি, ব্রিটিশ গণিতবিদ।
১৮৪৫ – গাব্রিয়েল লিপমান, ফরাসি-লুক্সেমবার্গীয় পদার্থবিজ্ঞানী এবং উদ্ভাবক।
১৮৬০ – মার্টিন হক, ইংরেজ শৌখিন ক্রিকেট তারকা ও অধিনায়ক।
১৮৮৮ – টমাস এডওয়ার্ড লরেন্স, ব্রিটিশ প্রত্নতত্ত্ব বিশারদ, সামরিক নীতি নির্ধারক ও লেখক।
১৮৯২ – মার্কিন কার্টুনিস্ট অটো মেসমার।
১৮৯৫ – অস্ট্রিয়ান অভিনেত্রী লিয়ান হেইড।
ইতিহাসের পাতায় আজকের দিনের ঘটনাবলী—-
২০০৮ – গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে পুরুষদের ৫০ মিটার ও মহিলাদের ৮০০ মিটার ফ্রিস্টাইল সাঁতার প্রতিযোগিতা শেষ হয়। মহিলাদের ৮০০ মিটার ফ্রিস্টাইল সাঁতার প্রতিযোগিতার ফাইনালে যুক্তরাজ্যের রেবেকা অ্যাডলিংটন হিটে তার করা নতুন অলিম্পিক রেকর্ড আবার ভেঙ্গে ৮:১৪.১০ সময়ে নতুন অলিম্পিক তথা নতুন বিশ্ব রেকর্ড গড়েন।
১৯০৪ – নিউ ইয়র্কে গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল স্টেশনের নির্মাণ কাজ শুরু।
১৯৪৬ – মুসলীম লীগ ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে পালনের সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কলকাতা দাঙ্গা শুরু হয়।
১৯৬০ – সাইপ্রাস দ্বীপ স্বাধীন হয়।
১৯৭২ – বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয় উগান্ডা।
১৯৭৫ – সৌদি আরব, সুদান কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান।
১৮২৫ – বলিভিয়ার প্রজাতন্ত্র ঘোষণা।
১৮৪৩ – ব্রাহ্মধর্মের প্রচার এবং তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষার উদ্দেশ্যে অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়।
১৮৫৮ – ব্রিটেনের রানি ভিক্টোরিয়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেমস বুচাননকে টেলিগ্রাফ পাঠান।
১৮৬৭ – কার্ল মার্কস ‘ক্যাপিটাল’ গ্রন্থের প্রথম খণ্ড লেখা শেষ করেন।
১৮৯৮ -এডউইন প্রেসকট রোলার কোস্টারের প্যাটেন্ট পান।
১৬৮৭ – জব চার্নকের সঙ্গে মোগল শাসনকর্তাদের চুক্তি স্বাক্ষরিত হলে ইংরেজরা সূতানুটিতে অস্ত্রাগার ও পোতাশ্রয় নির্মাণের অনুমতি লাভ করে।
এই দিনে মৃত্যুবরণ করেন যারা—-
২০০১ – ভারতীয় পদার্থবিদ ও আবহাওয়াবিজ্ঞানী আন্না মনি।
২০০২ – আবু নিদাল, ফিলিস্তিনি ফাতাহ: বিপ্লব পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা।
২০০৩ – ইদি আমিন, উগান্ডার প্রয়াত সামরিক স্বৈরশাসক।
২০১৬ – জোয়াও হ্যাভেলাঞ্জ, ব্রাজিলীয় ব্যবসায়ী ও ক্রীড়া কর্মকর্তা।
২০১৮ – ভারতরত্ন সম্মানে সম্মানিত অটল বিহারী বাজপেয়ী, ভারতের প্রাক্তন (দশম) প্রধানমন্ত্রী।
২০১৯ – পিটার ফন্ডা, মার্কিন অভিনেতা, পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার।
২০২০ – চেতন চৌহান ভারতের প্রথিতযশা সাবেক আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার।
১৯৪৮ – বেব রুথ, মার্কিন বেসবল খেলোয়াড়।
১৯৪৯ – মার্গারেট মিচেল, আমেরিকান লেখিকা ও সাংবাদিক।
১৯৫৭ – আর্ভিং ল্যাংমিউয়র, মার্কিন রসায়নবিজ্ঞানী ও পদার্থবিজ্ঞানী।
১৯৬১ – মৌলভী আবদুল হক, পাকিস্তানি পণ্ডিত এবং ভাষাতত্ত্ববিদ।
১৯৭৭ – এলভিস প্রেসলি, কিংবদন্তিতুল্য মার্কিন রক্ সঙ্গীত শিল্পী।
১৯৭৯ – জন জর্জ ডিফেনবাকার, কানাডার রাজনীতিবিদ এবং ১৩তম প্রধানমন্ত্রী।
১৯৯৭ – সুলতান আহমদ নানুপুরী, বাংলাদেশি দেওবন্দি ইসলামি পণ্ডিত ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব।
১৯৯৭ – নুসরাত ফাতেহ আলী খান, পাকিস্তানের কাওয়ালি সঙ্গীত শিল্পী।
১৮৮৬ – শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস, ঊনবিংশ শতকের এক প্রখ্যাত ভারতীয় বাঙালি যোগসাধক, দার্শনিক ও ধর্মগুরু।
১৮৮৮ – জন পেম্বারটন, আমেরিকান ঔষধ প্রস্তুতকারক।
১৮৯৯ – রবার্ট বুনসেন, জার্মান রসায়নবিদ।
।।তথ্য : সংগৃহীত ইন্টারনেট।।