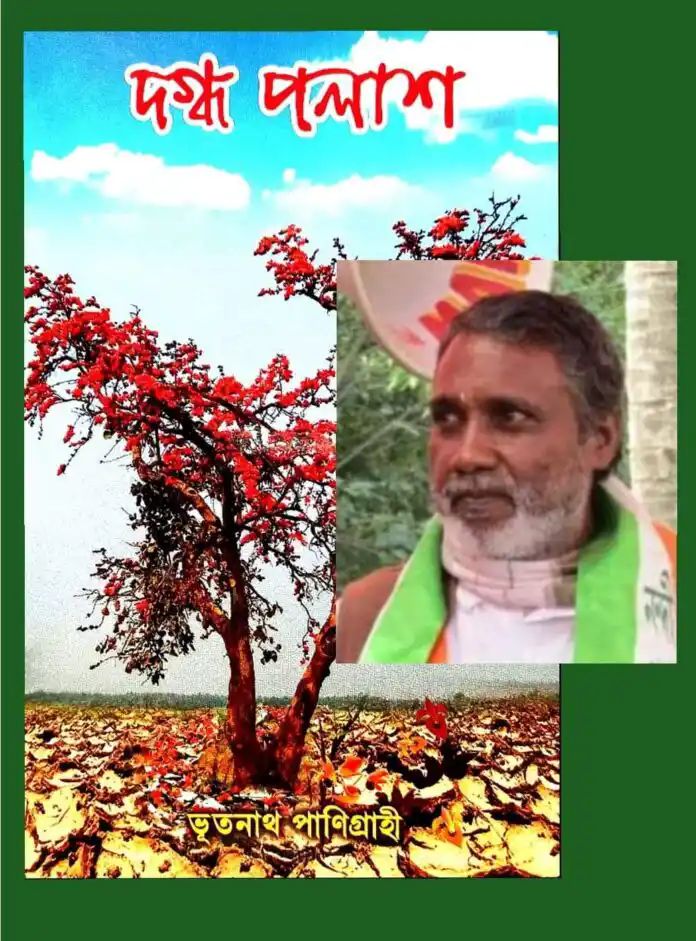বর্তমান প্রজন্ম তো দিলাম ছেড়েই ,
আমরা যতটা চিনি গ্যালিলিও , নিউটন , টেসলা কিংবা আইনস্টাইনকে ,
সুশ্রুত , ব্রম্ভগুপ্ত , চরক বা বরাহমিহিরকে ঠিক
ততটাই কি?
যতটা গর্বিত , উৎসাহিত , উত্তেজিত এনাদেরকে নিয়ে , ঠিক ততটাই আমাদের ভারতীয় কোহিনূরদের নিয়ে কি?
উত্তর বোধহয় হবে ‘না।’
আর হবেটাই বা কিভাবে?
অবহেলা , উদাসীনতা , সর্বোপরি
উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে রাজনীতি , বছরের পর বছর যদি গোড়াতেই ইংরেজদের মতন ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকে গলদ হয়ে , তো আমি-আপনি সাধারণ মানুষ আর করবোটাই বা কি?
গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় এ তো আজ পরিণত এক শক্তিশালী সিস্টেমে?
আর অন্ধ , বোবা , কালা হয়ে এই সিস্টেমের চাকায় পিষে বেঁচে থাকাটা আজ পরিণত হয়েছে বা করানো হয়েছে আমাদের অভ্যেসে , এরপর আদর্শ আর মনুষ্যত্ব বিক্রির সংখ্যাটা পৃথিবী উত্তপ্ত হওয়ার মতন বেড়ে চলেছে দিনের পর দিন ,
পাশাপাশি বহু বছর আর জন্মায়ও না রাজা রামমোহন রায় অথবা নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু।
অতএব আমার-আপনার বৃহত্তর সমাজটা না হয়
যাক ভবিষ্যতে কোমায় , আমি-আপনি সুখে
থাকলেই হল।
কিন্তু পরিণত হওয়া এ অভ্যেস আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মে একদিন সৃষ্টি করবেনা তো সুনামি?
যদি বলি চীনের উহান ইন্সটিটিউট অব ভাইরোলজি
থেকেই করোনা ভাইরাস মহাসংক্রমিত হয়ে প্রায় সমগ্র বিশ্বকে তছনছ করে ছেড়েছে?
ভেঙে টুকরো টুকরো করে ছেড়েছে পৃথিবীর বেশ কয়েকটা দেশের আর্থিক মেরুদণ্ড?
রাষ্ট্রের পর রাষ্ট্রকে বানিয়ে ছেড়েছে মৃত্যু উপত্যকা?
কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বিষয়টা বর্তমানে সিংহভাগ সাধারণ মানুষের কাছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে এমন যে , ও এক প্রকৃতিগত বিপর্যয় ছাড়া তেমন কিছুই ছিলনা , ওটা হতেই পারে।
সাথে আপনিসহ হাজার জন অন্তত আমায় পাল্টা
প্রশ্ন করবেন যে ,
নির্দিষ্ট বা উপযুক্ত তথ্য-প্রমাণ ছাড়া আপনি এ কথা এত আত্মবিশ্বাসের সাথে বলেন বা লেখেন কিভাবে?
প্রতিবেশী একটা রাষ্ট্রের সরকারের নামে এভাবে বদনাম দেন কিসের ভিত্তিতে?
সেক্ষেত্রে আপনাদের প্রশ্নদেরকে সম্মান জানিয়েই
আমি প্রত্যুত্তর করবো ,
দুর্ঘটনাবশতঃ কোনো কোনো সময়ে কিছু গোপনীয়
ঘটনার রহস্য ফাঁস হয়ে পড়ে কোনোভাবে ,
যেটা অনুসন্ধিৎসু লেখক-মন চিরুনী তল্লাশি করে খুঁজে নেয় ঠিকই।
আর কবর দেওয়া এরকম বহু কিছু আজ ইন্টারনেটের বাড়বাড়ন্তে বেরিয়ে এসে সাধারণ মানুষের কাছে বাধ্য হয়েছে ধরা দিতে।
ধরা যাক আমি ডাহা মিথ্যে বলছি , বা লেখায়
প্রয়োগ করতে চাইছি রাজনৈতিক কৌশল ,
তো জানাই , জাতিসংঘ স্বীকৃত এ বিশ্বের সব দেশকে ছাড়িয়ে চীন যে সবার মাথার উপরে উঠে আসতে চাইছে যেনতেন প্রকারেণ , এ বিষয়টা নিশ্চই কম-বেশি জানেন অনেকেই , আর বর্তমানে চীন যে ভারতের ঠিক কত বড় শত্রু , তা আর নিশ্চই যুক্তি , প্রমাণ দিয়ে কাউকে বোঝাতে হবেনা?
এরপরেও জানিয়ে রাখি , যদি সময় পান ,
গুগুলে গিয়ে সার্চ করে পড়বেন , ‘চক্রব্যূহে ভারত তথা বিশ্ববাসী।’
এছাড়াও রয়ে গেছে বেশ কিছু তথ্য-প্রমাণ , খোঁজার মতন খুঁজলে পাবেন আপনিও।
আচ্ছা কখনও কখনও আপনাদের মনে আমার
মতন প্রশ্ন নিশ্চই জাগে যে ,
Research and Analysis Wing , Mossad , Central Intelligence Agency , Australian Secret Intelligence Service ইত্যাদি বিশ্বের তাবড়-তাবড় সব গোয়েন্দা সংস্থা , জাতিসংঘ ,
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বর্তমানে সব চুপ কেন?
বিশ্বব্যাপী করোনা ভাইরাস সংক্রমণের উৎসটা
ঠিক কোথায় , তা শুধুমাত্র খুঁজে বের করাটা কি
অবৈধ কিংবা ঘোরতর অন্যায় কিছু ছিল?
এটা কি সত্যিই ছিল না সাধারণ মানুষের জানার একটা অধিকার?
লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের বিশ্বাস , জীবন , আস্থা , আর্থিক পরিস্থিতি প্রভৃতির চেয়ে রাজনীতিটা কি এক্ষেত্রেও বড়?
তবে কি বিশ্বব্যাপী কমিউনিস্টের চাপ?
না কি ভয়-ভীতি , না আন্তর্জাতিক সম্পর্ক খারাপ হওয়ার দুশ্চিন্তা?
কিভাবে এত বিপুল সংখ্যক জনগণ আজ বাধ্য হয়ে হলেও মেনে নিল এই অমানুষিক হত্যাযজ্ঞকে?
যদি বলি মানুষ ছাড়াও এ অনন্ত বিশ্বব্রম্ভাণ্ডে মানুষেরই মতই আছে একধরণের প্রাণীর অস্তিত্ব?
আর হতে পারে মুষ্টিমেয় কিছু জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের
অতিরিক্ত আগ্রহ থেকে জন্ম নেওয়া দিবারাত্রির নিরলস এক্সপেরিমেন্ট , তা থেকে রেডিও সিগনাল পাঠানো , এর ভয়াবহ পরিণাম হিসেবে অতিরিক্ত মাশুল গুণতে হতে পারে গোটা পৃথিবীবাসীকেই?
হতে পারে ভবিষ্যতে এ গ্রহ থেকে সমগ্র মানব সভ্যতার অস্তিত্বই নিশ্চিহ্ন?
বলাবাহুল্য স্টিফেন হকিং তো আগেই এ বিষয়ে সচেতন করে দিয়ে গেছেন বিজ্ঞানীদের।
সময় করে কিছুটা হলেও ঘুরে আসতে পারেন গুগুল থেকে , টাইপ করবেন , ‘গহীন ও দুর্ভেদ্য রহস্যে আবৃত
Area-51!’
এছাড়াও লুকিয়ে আছে বেশ কিছু উপযুক্ত তথ্য-প্রমাণ , যা অনেকেই আজ গেছেন জেনে , কিন্তু ওই , চুপ?
ভারতের মাটিতেই চাপা দিয়ে রাখা আছে এমন কিছু ইতিহাস , যা সশরীরে ভূমি ফুঁড়ে জনসমক্ষে বেরিয়ে আসলে বোধহয় সৃষ্টি হবে দাবানল।
তো যাইহোক , ফিরে আসি সেই আগের টপিকে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিনের ডেভিড ফ্রলি , বর্তমানের পদ্মভূষণ প্রাপ্ত , বেদাচার্য , আয়ুর্বেদিক শিক্ষক , বৈদিক জ্যোতিষ , গবেষক ও লেখক
বামদেব এক বিখ্যাত উক্তি করেছিলেন যে ,
“যখন পুরো বিশ্ব লেখাপড়া জানতো না , তখন ভারতের হিন্দুরা বেদ লিখেছিলেন।
যখন পুরো বিশ্বে শিক্ষা চালু ছিল না , তখন ভারতের হিন্দুদের শিক্ষা দেওয়া হত গুরুকুলের মাধ্যমে।”
ভারতের মহান পরমাণু বিজ্ঞানী ও একাদশ রাষ্ট্রপতি ডঃ এ পি জে আব্দুল কালাম এ প্রসঙ্গে উক্তি করেছেন , “বেদ মানবসভ্যতার প্রাচীনতম ক্ল্যাসিক , ভারতবর্ষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ।
সমগ্র ভারতের আত্মা এই বেদেই প্রোথিত।”
ভলতেয়ার বলেছেন ,
“বেদ হল মানবসভ্যতার সবচেয়ে মূল্যবান উপহার , যার জন্য পাশ্চাত্য সবসময় প্রাচ্যের নিকট কৃতজ্ঞ থাকবে।”
বেদে সংখ্যাতত্ত্বের সর্বপ্রথম উল্লেখ প্রসঙ্গে আইনস্টাইন মন্তব্য করেছিলেন ,
“আমরা আর্যদের কাছে কৃতজ্ঞ , কেননা তাঁরাই সর্বপ্রথম সংখ্যা আবিস্কার করেছে যা ছাড়া বিজ্ঞানের কোনো আবিষ্কারই সম্ভবপর হত না।”
দার্শনিক , ধর্ম এবং সমাজতত্ত্ববিদ , অধ্যাপক , ভারতবিশারদ , সংস্কৃত ভাষায় সুপ্রসিদ্ধ জার্মান পণ্ডিত ও অনুবাদক ম্যাক্স মুলার বলেছেন ,
“পৃথিবীতে বেদ-উপনিষদের মত প্রণোদনাপূর্ণ ও
এত অতিমানবীয় বই আর নেই।”
জাতি , ধর্ম , বর্ণ নির্বিশেষে সর্বধর্মসমন্বয়ের দেশ আমাদের ভারতবর্ষ , যা বিশ্ব ইতিহাসে দখল করে আছে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান , কিন্তু আজ ক্রমশ
যেন আত্মপ্রকাশ করছে তা কেমন ম্লান হয়ে।
তো যাইহোক , বিশ্ববন্দিত , মহান মানুষদের এই অমূল্য মন্তব্যসমূহ এখানে তুলে ধরার উদ্দেশ্য কোনো ধর্মের জয়গান গাওয়া বা প্রচার নয় ,
বরং অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানানো এই যে ,
এই সমস্ত কিংবদন্তি , ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বদের অমূল্য সৃষ্টি ও এর পিছনে লুকিয়ে থাকা অক্লান্ত ও নিরলস পরিশ্রম , সংগ্রামের সেইসব কাহিনী , আত্মত্যাগ আজও ভারতীয় ইতিহাসের পাতায় পেয়ে ওঠেনি সেভাবে বিশেষ কোনো জায়গাই , এমনকি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র , চন্দ্র শেখর আজাদ বা রাসবিহারী বসুকে নিয়েও নয়।
থেকে গেছে অবহেলা , উদাসীনতা , বঞ্চনা , সর্বোপরি
রাজনীতির স্বীকার হয়ে , আর এভাবেই ধীরে ধীরে হয়তো ডাইনোসরের মতন এনারা হয়ে যাবেন ভারতের ভূখণ্ড থেকে আগামীতে বিলুপ্ত।
এ প্রজন্মকে যদি প্রশ্ন করা হয় , ‘পৃথিবীর প্রথম সার্জন
কে ছিলেন , যিনি আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতকেই
ব্যবহার করতেন প্রায় ১১৬-২০ রকমের ছুরি-কাঁচি?’
কিংবা ‘Father of Surgery কাকে বলা হয়?’
নতুন প্রজন্ম কেন , আমরাই অনেকেই ঠিক জানিনা এর সঠিক উত্তর , এ আমাদের চরম লজ্জা!
আমরা হয়তো এও জানিনা বা স্মৃতিতে নেই আজ আর বেঁচে যে , সম্পূর্ণ পৃথিবীতে যখন প্রথাগত শিক্ষার কোনো অস্তিত্বই ছিল না , তখন ভারতে ছিল ১৬ টা বিশ্ববিদ্যালয় ও ৭২৫ টা কলেজ।
দেশীয় সেই সমস্ত মহামানবকে আমরা যথাযথ মর্যাদা দিতে পারিনি ঠিকই , কিন্তু রতনে ঠিকই চিনে নিয়েছে রতন।
অস্ট্রেলিয়ার মেলবর্নের Royal Australia College of Surgeons – এর ঠিক সামনেই সগৌরবে আজও বসে আছেন মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পুত্র এবং ধন্বন্তরির শিষ্য সুশ্রুত এর শ্বেত পাথর মূর্তি।
রাজনীতি , বিনোদন , অপরাধ , খেলাধুলা , প্রতিদিনের পেপার , নিউজ চ্যানেলে এসব
দেখে-শুনে যেন অস্থির ও তিক্ত হয়ে গেছে মন ,
পরিণত হয়ে গেছে বা পরিণত করানো হয়েছে এ আমাদের এক অভ্যেসে।
তাই প্রকৃত গণতন্ত্র , শিক্ষা-সংস্কৃতি তথা ভারতীয় অতীত ইতিহাসের সেই গৌরবময় , ভাস্বর এবং সুবৃহৎ অধ্যায় আবার ভারতবাসীর কাছে ফিরে আসুক স্বমহিমায় , এই আশায় বুক বেঁধে আজ নয় আপাতত এখানেই শেষ হোক এই প্রবন্ধ।