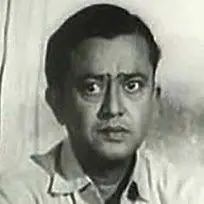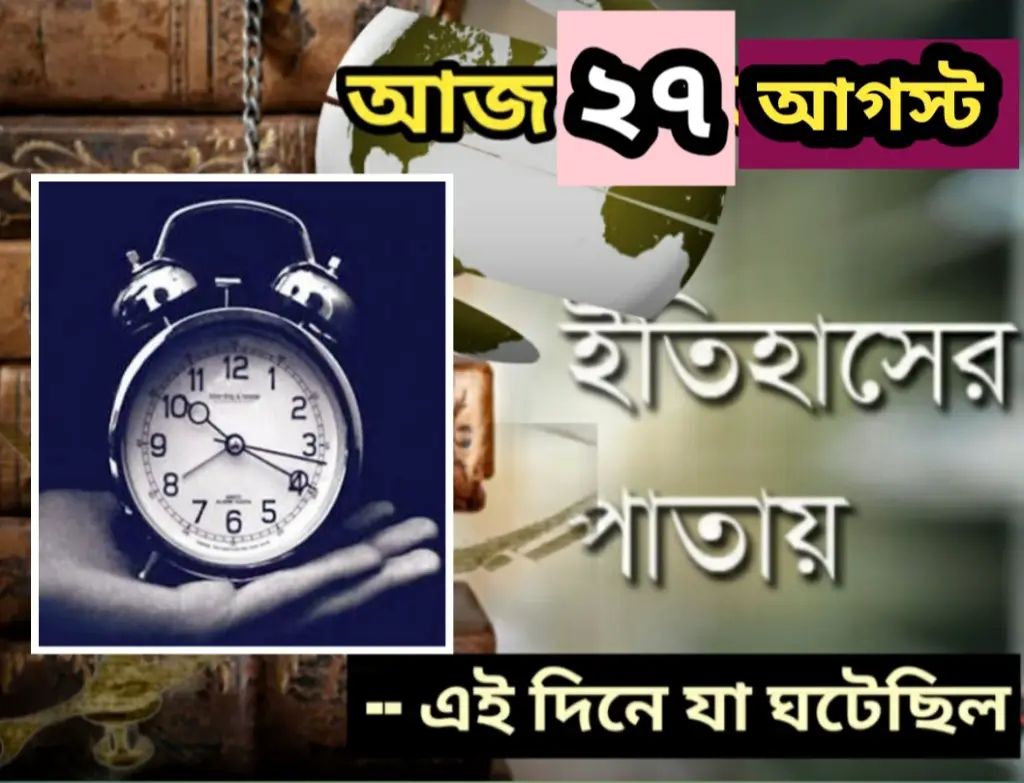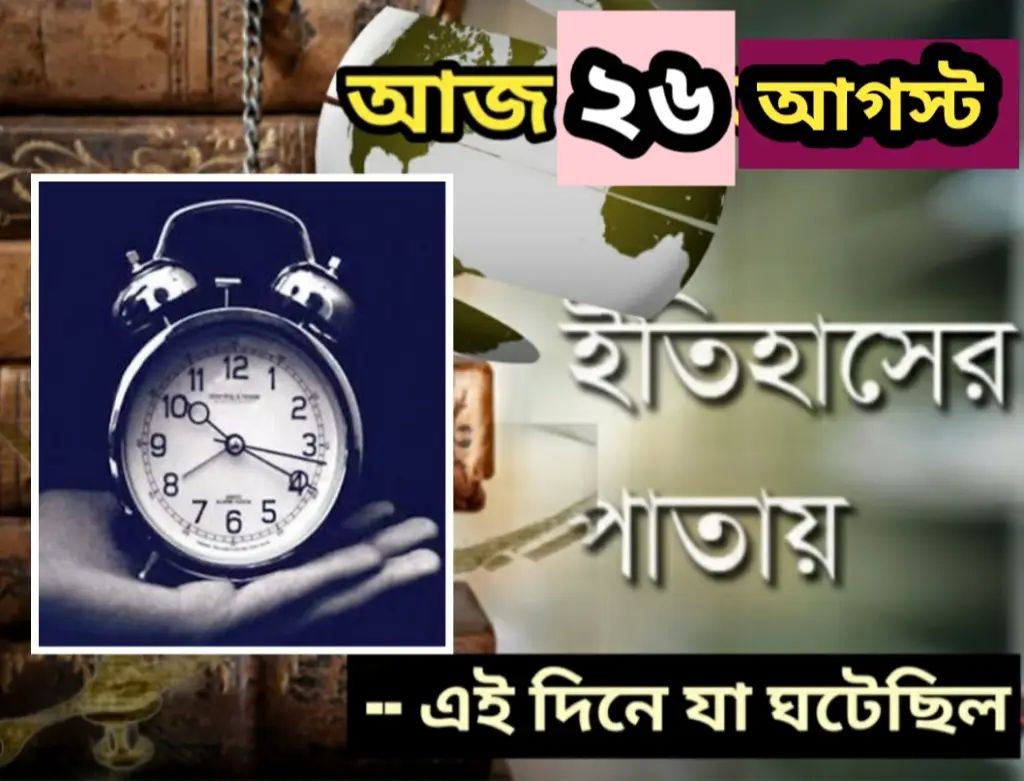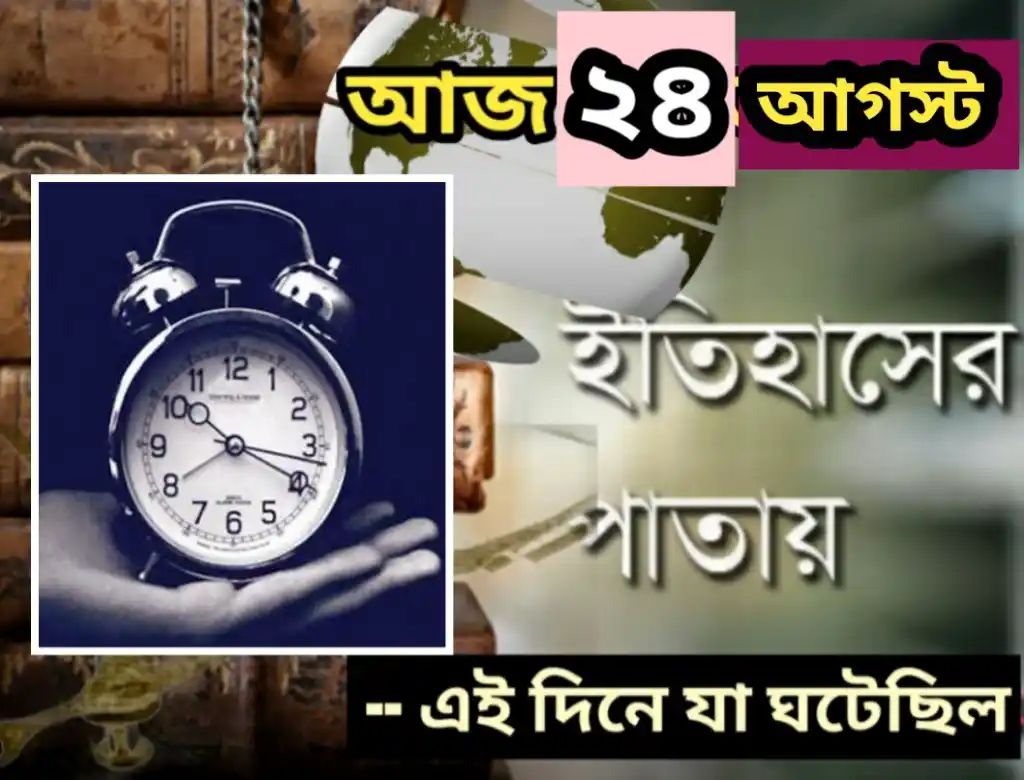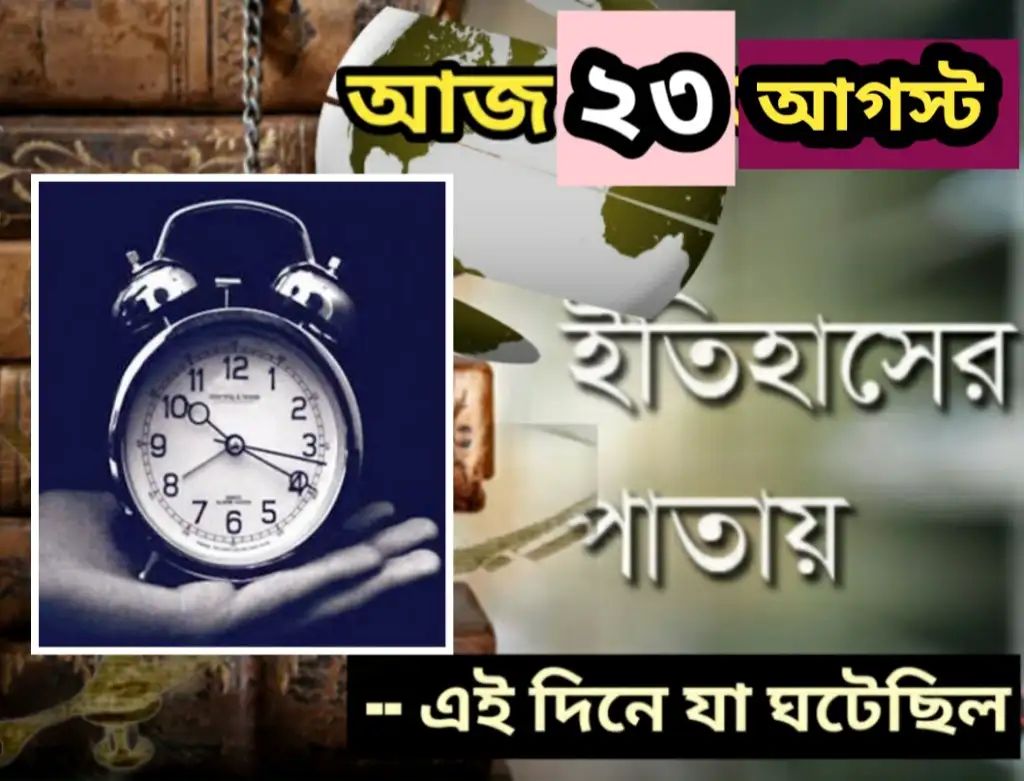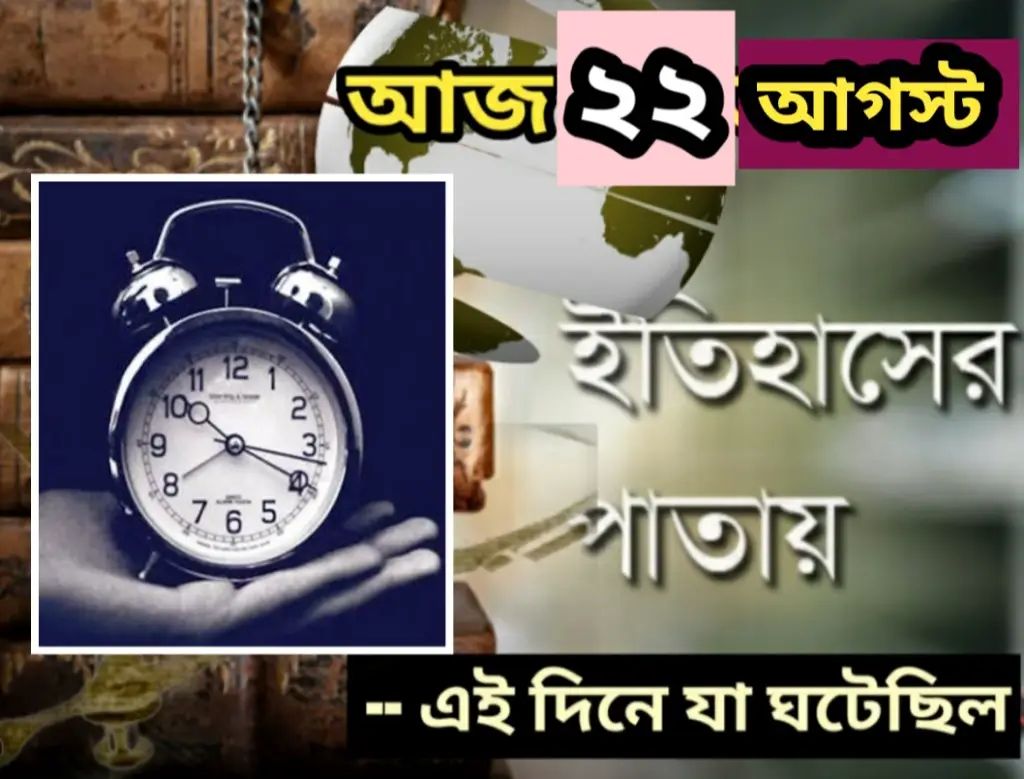ওঁ নমঃ শ্রী ভগবতে প্রণবায়….!
ওঁ গণ গণপতয়ে নমঃ,…
আমাদের সুন্দর মূল্যবান মনুষ্য জীবনে উৎসবমুখর ভারতবর্ষে পূণ্যভূমি পবিত্রভূমি এই তপভূমিতে জগৎ জননী মায়ের আসার আগেই শ্রী গণপতি বাপ্পা আসেন। সত্য সনাতন ধর্মে যে কোনো শুভকাজের শুরুতে তিনি পূজিত হন এবং সফলতার প্রতীক হিসেবেও বিবেচিত হন। গণেশ বা গজানন হলেন শিব ও পার্বতীর পুত্র। আগামী শুক্লাচতুর্থী বা গণেশচতুর্থী তিথিতে গণপতি বাপ্পার আগমন ঘটবে সেই *গণেশ পূজা* চলবে দশদিন অনন্ত চতুর্দশী পর্যন্ত। গণেশ বিঘ্ননাশকারী, বুদ্ধি ও জ্ঞানের দেবতা, শিল্প ও বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষক, এবং সৃষ্টি ও সৌভাগ্যের প্রতীক। সত্য সনাতন ধর্মে যে কোনো শুভকাজের শুরুতে তিনি পূজিত হন এবং সফলতার প্রতীক হিসেবেও বিবেচিত হন।
“গণেশ” নামটি গণ ও ঈশ শব্দ দুটির সমষ্টি। গণ শব্দের অর্থ গোষ্ঠী বা সমষ্টি এবং ঈশ শব্দের অর্থ ঈশ্বর বা প্রভু। ভগবান গণেশ এই মহাবিশ্বে শৃঙ্খলা আনেন এবং কোনও নতুন প্রচেষ্টা, বৌদ্ধিক যাত্রা বা ব্যবসায়িক উদ্যোগ শুরু করার আগে সকলেই তাঁর উপাসনা করেন। তিনি সমস্ত বাধা বিঘ্ন দূরকারী ভগবান হিসাবে পরিচিত। গণেশ উৎসব বা গণেশ চতুর্থী ভগবান গণেশের জন্মোৎসব। তিনি বিঘ্ননাশক, জ্ঞান ও সমৃদ্ধির দেবতা, তিনি মর্ত্যে অবতীর্ণ করে ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। তিনি গণপতি, বিঘ্নেশ্বর, বিনায়ক, গজপতি, একদন্ত ইত্যাদি নামেও পরিচিত। এই উৎসবের মাধ্যমে গণেশের জন্মকে স্মরণ করা হয়। এটি একটি আনন্দময় ও পারিবারিক সামাজিক, সার্বজনীন সামাজিক অনুষ্ঠান। মন্ডপে গণেশের মূর্তি স্থাপন করে পূজা করা হয় এবং বিভিন্ন ধরনের মোদক ও মিষ্টি নিবেদন করা হয়।
পৌরাণিক তথ্য অনুযায়ী দেবী পার্বতী যখন স্নান করতে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি নিজের শরীর থেকে ঘর্ষণের মাধ্যমে মাটি ও আবর্জনার মিশ্রণ থেকে গণেশকে সৃষ্টি করেন এবং তাকে নিজের বাড়ির পাহারাদার হিসেবে নিযুক্ত করেন। গণেশ বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিলেন, যখন তার পিতা শিব ঘরে ফিরতে চাইলেন গণেশ তাকে বাধা দেন। ফলে তাদের মধ্যে যুদ্ধ হয় এবং শিব গণেশকে এমনভাবে আঘাত করেন যে তার মাথা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই ঘটনার পর দেবী পার্বতী অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে পড়েন এবং শিবকে গণেশকে পুনরুজ্জীবিত করতে বলেন। তখন শিব তার প্রথম যে প্রাণীটিকে দেখতে পান, তার মাথা কেটে গণেশের শরীরে প্রতিস্থাপন করেন। আর সেই প্রাণীটি ছিল একটি হাতি। তাই তিনি গজানন।
ভারতবর্ষে ১৮৯৩ সালে ব্যাপকভাবে গণেশ উৎসব বা গণপতি উৎসবের প্রচলন করেন মহান স্বাধীনতা সংগ্রামী লোকমান্য তিলক বা বাল গঙ্গাধর তিলক। তিনি এই উৎসবকে জনগণের মধ্যে ঐক্যের প্রচার এবং জাতীয়তাবাদের ধারণা কে উজ্জীবিত করার জন্য শুভারম্ভ করেন। যা পরবর্তীতে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পরবর্তীকালে নেপাল, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া (জাভা এবং বালি), সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, বাংলাদেশ, ফিজি, গায়ানা, মরিশাস এবং ত্রিনিদাদ ও টোবাগো সহ বৃহৎ জাতিগত ভারতীয় জনসংখ্যার দেশগুলিতে গণেশ পূজার প্রথা বিস্তার লাভ করেছে।
ভাদ্র মাসের শুক্ল চতুর্থীতে শুরু হয় এবং উৎসবের সময়কালে গণেশের মূর্তি স্থাপন, পূজা ও শোভাযাত্রার মাধ্যমে আনন্দ ও ভক্তির প্রকাশ ঘটে। উৎসবের মূল অনুষ্ঠানগুলো মহারাষ্ট্র ও গুজরাটের মতো রাজ্যগুলিতে অত্যন্ত জনপ্রিয় ও জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালিত হয়, যেখানে এই উৎসবকে জাতীয় ঐক্যের প্রতীক হিসেবেও দেখা হয়। এটি শুধু একটি ধর্মীয় উৎসবই নয়, এটি ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, জাতীয় ঐক্য এবং ভক্তির একটি জীবন্ত উদাহরণও বটে। গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের পাশাপাশি ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও এই উৎসব অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে পালিত হয়। এই বৎসর ২৭শে আগস্ট বুধবার গণেশচতুর্থীর দিন উৎসব শুরু হবে। এবং ৬ ই সেপ্টেম্বর শনিবার অনন্ত চতুর্দশীর দিন উৎসবের সমাপ্তি হবে। গণপতি বাপ্পা সকল বাধা বিঘ্ন নাশ করে সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন। সুখ সমৃদ্ধি সৌভাগ্য বৃদ্ধি করুন এই প্রার্থনা করি। জগৎগুরু ভগবান স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের শুভ ও মঙ্গলময় আশীর্বাদ সকলের শ্রী বর্ষিত হোক।
*গণপতির প্রতিষ্ঠা মুহুর্ত:-*
২৭শে আগস্ট, ২০২৫, বুধবার গণেশ চতুর্থীর শুভ মুহূর্ত হলো সকাল ১১:০৬ থেকে দুপুর ১:৪০ পর্যন্ত, যা গণপতিকে বাড়িতে আনার এবং স্থাপনার জন্য সবচেয়ে শুভ সময় হিসাবে বিবেচিত হয়। এই সময়ে, বিশেষত দুপুরবেলা, সিদ্ধিদাতা গণেশের জন্ম হয়েছিল বলে বিশ্বাস করা হয়, তাই এই সময়টি ‘মধ্যাহ্ন গণেশ পূজা’র জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আসলে, বুধবার সকালে সূর্যোদয় থেকে পুরো দিনটি শুভ। সুবিধামতো গণপতির প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। সর্বাধিক শুভ মুহুর্ত- অভিজিৎ মুহুর্ত ২৭শে আগস্ট ১১.৪৫ থেকে ১২.৫৫ পর্যন্ত হবে। এই মুহুর্তে গণপতি মূর্তি স্থাপন সবচেয়ে শুভ হবে। এর পাশাপাশি, ২৭শে আগস্ট দুপুর ১.৩৯ মিনিট থেকে সন্ধ্যা ৬.০৫ মিনিট পর্যন্ত মুহুর্তটিও শুভ।
ওঁ গুরু কৃপা হি কেবলম্ ।
স্বামী আত্মভোলানন্দ *পরিব্রাজক*