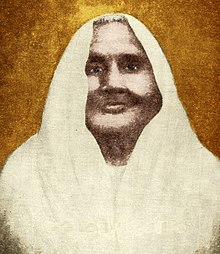সুপ্রিয়া দেবী (৮ জানুয়ারী, ১৯৩৩), একজন বাঙালী অভিনেত্রী, যিনি বাংলা চলচ্চিত্রে ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে অভিনয় করেন। তার আসল নাম কৃষ্ণা এবং ডাকনাম বেনু। উত্তম কুমারের সঙ্গে ‘বসু পরিবার’ ছবিতেই বড় পর্দায় তাঁর আত্মপ্রকাশ। ‘মেঘে ঢাকা তারা’ ছবিতে তাঁর অনবদ্য অভিনয় এখনও সবার হৃদয়ে গেঁথে রয়েছে ৷ মোট ৪৫টি ছবিতে তিনি অভিনয় করেন
সুপ্রিয়া দেবী মায়ানমারের মিয়িত্কিনায় জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা বিখ্যাত আইনজীবী গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, বার্মায় বসবাসরত অনেক ভারতীয় ভারতে চলে আসেন। সুপ্রিয়া দেবীর পরিবার শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ কলকাতায় বসবাস শুরু করেন।
সুপ্রিয়া দেবী তার বাবার নির্দেশিত দুটি নাটকে অভিনয় করে সাত বছর বয়সে তার অভিনয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনি ছোটবেলা থেকেই নাচের প্রতি খুব আগ্রহী ছিলেন, এমনকি তিনি থাকিন নু থেকে একটি পুরস্কার জিতেছিলেন। শৈশবকাল থেকেই তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন নীহার দত্ত, যিনি গুহ ঠাকুরতা পরিবারের একজন সদস্যকে বিয়ে করেছিলেন এবং মিসেস নীহার গুহ ঠাকুরতা নামে পরিচিত ছিলেন, যিনি সেই সময়ে বার্মার একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী ছিলেন।
১৯৪৮ সালে, ব্যানার্জি পরিবার ভালোর জন্য কলকাতায় পুনর্বাসিত হয়। তারা ১৯৪২ সালে শরণার্থী শিবিরে বসবাস করত, যখন জাপান জোরপূর্বক বার্মা দখল করে। যুবতী সুপ্রিয়া ও তার পরিবার জোর করে পায়ে হেঁটে কলকাতায় ফিরতে বাধ্য হয়।
কলকাতায়, তিনি তার নাচের প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখেন এবং গুরু মুরুথাপ্পান এবং পরে গুরু প্রহ্লাদ দাসের কাছ থেকে নৃত্যের প্রশিক্ষণ নেন। সুপ্রিয়া দেবী এবং তার পরিবারের সাথে বিখ্যাত অভিনেত্রী চন্দ্রাবতী দেবীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল।
১৯৫৪ সালে, সুপ্রিয়া দেবী বিশ্বনাথ চৌধুরীকে বিয়ে করেন এবং পরে তাদের একমাত্র কন্যা সোমা জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৫০ এর দশকের শেষের দিকে একটি বিখ্যাত চলচ্চিত্র দিয়ে ফিরে আসার আগে তিনি কিছু সময়ের জন্য চলচ্চিত্র থেকে অবসর নিয়েছিলেন।
নানা চরিত্র, সে সব চরিত্রের বৈচিত্রময়তা সুপ্রিয়া দেবীকে বসিয়েছে এক ভিন্ন আসনে। এর মধ্যে বহু ছবিতেই তাঁর বিপরীতে ছিলেন বাংলা ছায়াছবির আর এক কিংবদন্তি অভিনেতা উত্তম কুমার। তাঁর সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দিয়ে অভিনয় করাটা বড় সহজ কথা নয়। কিন্তু সুনিপুণ দক্ষতায় দু’জনের এক আশ্চর্য রসায়ন তৈরি হয়েছিল পর্দায়। এএর পর তাদের মধ্যে ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তারপর থেকে তারা বহু বছর ধরে একসাথে থাকতেন।
তাঁর চলচ্চিত্র সমূহ —–
দেবদাস, দুই পুরুষ, সন্ধ্যা রাগ, সন্ন্যাসী রাজা, যদি জানতেম, বাঘবন্দী খেলা, বনপলাশীর পদাবলী, চিরদিনের, দ্য নেমসেক, একটী নদীর নাম, শেষ ঠিকানা, মন নিয়ে, চৌরঙ্গি, তিন অধ্যায়, কাল তুমি আলেয়া, শুধু একটি বছর, হানিমুন, ইমান কল্যাণ, কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী, আপ কি পরিছাঁইয়া, দূর গগন কি ছাঁও মে, লাল পাত্থর, বেগানা, নতুন ফসল, শুন বর নারী, বসু পরিবার, সূর্য শিখা, কোমল গান্ধার, মধ্য রাতের তারা, মেঘে ঢাকা তারা। এত অজস্র চরিত্রের মধ্যেও সুপ্রিয়া চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন ঋত্বিক ঘটকের ছবি ‘মেঘে ঢাকা তারা’ ও ‘কোমলগান্ধার’-এ তাঁর কাজের জন্য। বাঙালির বড় আপন এই অভিনেত্রী বেঁচে থাকবেন তাঁর অভিনীত চরিত্রগুলির মধ্যেই।
তিনি ২০১১ সালে বঙ্গভূষণ পুরস্কার অর্জন করেন, যা পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ বেসামরিক উপাধি। ২০১৪ সালে বাংলা চলচ্চিত্রে তার অবদানের জন্য ভারত সরকার সুপ্রিয়া দেবীকে, ভারতের চতুর্থ সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কার “পদ্মশ্রী” তে ভূষিত করেন।
২০১৮ সালের ২৬ জানুয়ারি এই মহান অভিনেত্রী কলকাতায় ৮৫ বছর বয়সে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। টলিউড ইন্ডাষ্ট্রির কাছে তিনি সকলের প্রিয় ‘বেনু দি’। কিংবদন্তি অভিনেত্রীর অভিনয় ক্যারিশ্মা নিয়ে আলোচনা নেহাতই বাতুলতা। তিনি চলে গিয়েছেন ছয় বছর হল৷ তবে সিনেপ্রেমী বাঙালির মননে তিনি থেকে যাবেন আজীবন।
।। তথ্য : সংগৃহীত উইকিপিডিয়া ও বিভিন্ন ওয়েবসাইট।।