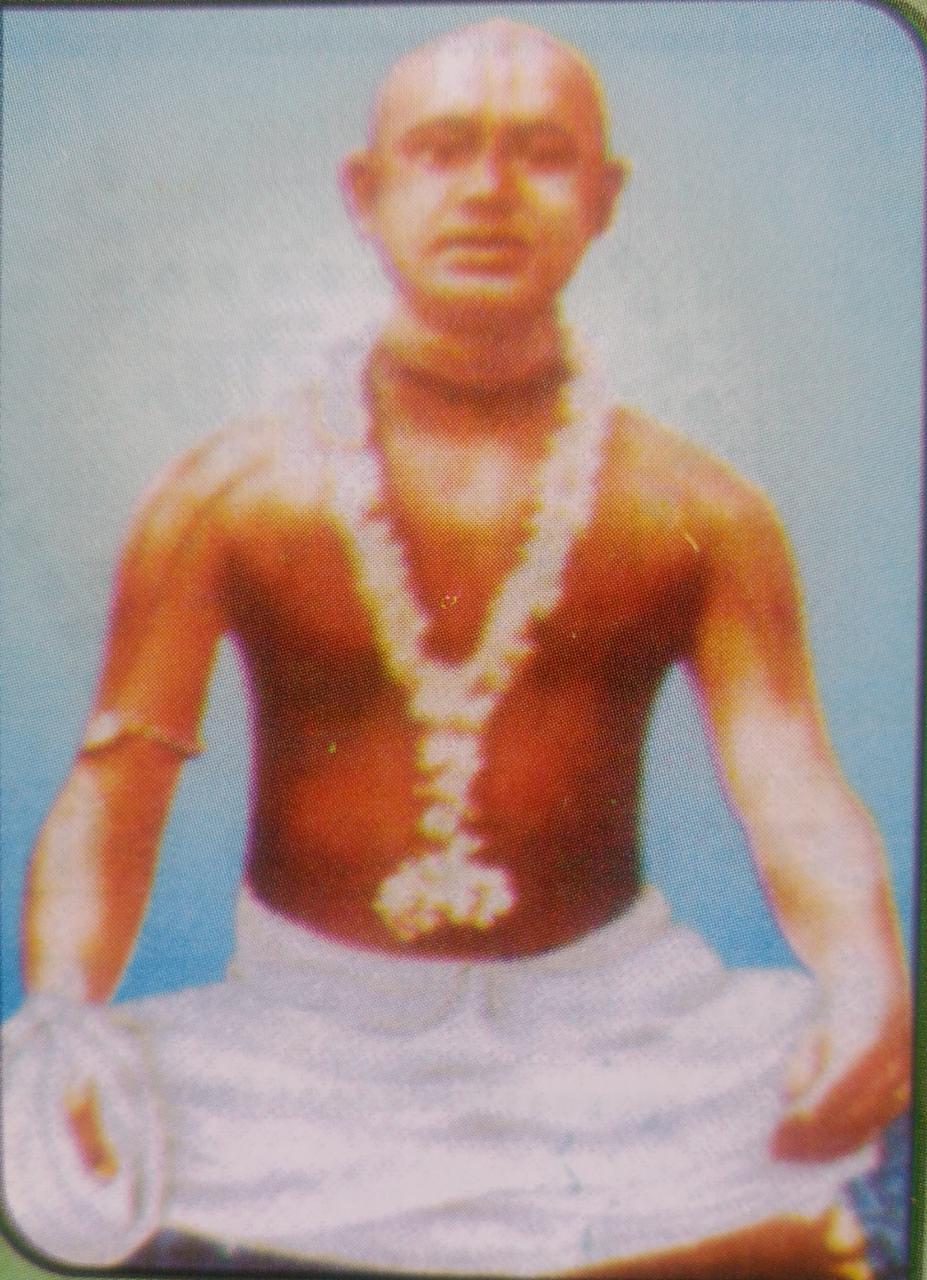বিশ্ব বাবা দিবস আজ। বিশেষ এই দিনটিতে বাংলাদেশের বাবা মায়েরা ভালো
আছেনতো? সন্তানের কষ্টে কারো চোখের জল ঝড়ছে নাতো? বিনা চিকিৎসায় আর
অনাহারে নেইতো কেউ? আপনারা কেউ বৃদ্ধাশ্রমে আছেন কি? মনের কোনে উঁকিঝোকি
মারে এইসব প্রশ্ন। প্রশ্ন জাগার কারন আছে। পত্রিকার শিরোনাম যদি এমন হয়-
‘ডাস্টবিন থেকে উদ্ধার করা অসুস্থ বৃদ্ধ পিতাকে বৃদ্ধাশ্রমে প্রেরণ’;
অন্যটির শিরোনাম ’ ‘বাসস্ট্যান্ডে ফেলে রাখা বৃদ্ধ মায়ের ছেলের জন্য
অপেক্ষায় কাটলো একমাস’। তাহলেতো প্রশ্ন জাগবেই। সংবাদ দুটি আমাদের
বিবেক, মূল্যবোধ, পারিবারিক বন্ধন এবং আত্মার সম্পর্ক বিষয়ক এতদিনকার
ধ্যান ধারণার ওপর প্রচন্ড আঘাত হানে। সংবাদ দু’টি সমাজের এক নগ্ন
বাস্তবতাকে উন্মোচন করে। হালযুগে বাবা-মায়ের প্রতি সন্তানদের সন্তানদের দ্বায়ীত্ববোধ কমতে শুরু
করেছে। সবাই কেমন যেন ব্যস্থ হয়ে ওঠেছে। স্বার্থপরতো বটেই। তাই অনেক বাবা-মায়ের আশ্রয় হয় এখন বৃদ্ধাশ্রমে। আজকাল বৃদ্ধাশ্রমের সাথে বেশ
পরিচিত আমরা। এক দশক আগেও অধিকাংশ মানুষের মধ্যে বৃদ্ধাশ্রমের তেমন ধারণা ছিলো না। এখন দেশের অনেক জায়গায়ই বৃদ্ধাশ্রম গড়ে উঠেছে। আর নরক নামীয় এ বৃদ্ধাশ্রমে আশ্রয় হচ্ছে অনেক বৃদ্ধ পিতা-মাতার। সেখানে যেতে তাদের বাধ্য করা হয়। অনেকে আবার জন্মদাতা পিতা-মাতার জন্য অতটুকুও ভদ্রতাও দেখান না। ওরা জন্মদাত্রীকে ফেলে আসেন রাস্তঘাটে, নর্দমায়। ঐপশুরা আমাদের অতি শ্রদ্ধেয় মুরব্বিদের কখনোবা ডাস্টবিনে ফেলে আসতেও দ্বিধা করেন না। এমন ঘটনা কতটা অমানবিক, কতটা বিবেকবর্জিত এবং আপত্তিকর, সেটা সহজেই বুঝা যায়।
এই অমানবিক বিষয়গুলোকে আমাদের সামনে আনা উচিৎ। সমাজ, রাষ্ট্র এবং পরিবারের অপরাপর লেখকদের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে প্রতিরোধ গড়ে তোলা উচিত। এ নিয়ে আন্দোলন হতে পারে। পরিবারের লোকজন এ আন্দোলনে শামিল হবেন,
প্রতিবেশীরা যোগ দেবেন। রাষ্ট্রেরও এ ব্যাপারে দায় আছে। রাষ্ট্র এমন অমানবিক বিষয়কে আইনের আওতায় আনতে পারে। নিয়োজিত ম্যাজিস্ট্রেটদের মাধ্যমে ভ্রাম্যমাণ আদালত গঠন করে কু-সন্তান কিংবা কু-পুত্রবধুদের তাৎক্ষণিক ৬ মাস কিংবা ততোধিক সময়ের জন্য সাজা দিতে পারে না। বিষয়গুলো জনসমক্ষে নিয়ে আসা রাষ্ট্রের নাগরিক হিসাবে আমাদেরও কর্তব্য আছে। পরিবারের অন্য সদস্য,
প্রতিবেশীরা এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে তার কর্মস্থলে গিয়ে প্রতিবাদ জানাতে পারেন। লিখিত অভিযোগ দিতে পারেন। মোদ্দা কথা হলো, সকলকে
সকলের জায়গা থেকে ওদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে হবে, প্রতিবাদ করতে হবে, প্রতিরোধ গড়তে হবে। সবচেয়ে ভালো হয় নিজেরা নিজেদের থেকে ভালো হয়ে গেলে। ভাবনায় আনতে হবে, আমরা আমাদের পিতা-মাতার কারণেই পৃথিবীতে আসতে পেরেছি।
তাঁরাই আমাদের আলোর মুখ দেখিয়েছেন। তাঁরাই আমাদের আগুন, পানি, রোদ-বৃষ্টি
থেকে রক্ষা করেছেন। শিক্ষা দিয়েছেন, দিনদিন বড় করে তুলেছেন। মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন; যদিও আমরা অনেকে মানুষ না হয়ে
অমানুষই হয়েছি।
আমরা অমানুষ হয়ে যাচ্ছি বলেই আমাদের মা-বাবারা আমাদের সেবা থেকে বঞ্চিত
হচ্ছেন। ‘আপনের চেয়ে পর ভালো, পরের চেয়ে বৃদ্ধাশ্রম।’ কঠিন এক সত্য। আর এ
সত্যকে মেনেই অনেক বৃদ্ধ মা-বাবা আশ্রয় নেন বৃদ্ধাশ্রমে। সন্তানের কাছে
যাদের বেশি কিছু চাওয়ার নেই; শেষ বয়সে আদরের সন্তানের পাশে থেকে সুখ-দুঃখ
ভাগ করবার ইচ্ছা এতটুকুই যা চাওয়ার। আর এ নিয়েই প্রতিটি পিতা-মাতা প্রহর
গুনতে থাকেন দিবা-রজনী। কিন্তু অনেকেরই সেই সন্তানের কাছে আশ্রয় না হয়ে;
আশ্রয় হয় আপনজনহীন বৃদ্ধাশ্রমে। শেষ বয়সে ঘরের কোণেও জনমদুখী মা-বাবার
এতটুকুও জায়গা মিলে না। ওদের ছুঁড়ে দেয়া হয় প্রবীণ নিবাসনামীয় নরকে। তবুও
প্রতিবাদ দানা বাঁধে না; মন অভিশাপ দেয় না। নাড়ী ছেঁড়া ধন ওরা। তাই চুপ
থাকেন, একেবারে চুপ। তবে এ নিষ্ঠুরতা তাদের কেবলই কাঁদায়। এ কেমন নিয়তি?
ভাবি আমরা কতটাই না আধুনিক স্বার্থপর!
“বৃদ্ধাশ্রম থেকে সন্তানের কাছে মায়ের চিঠি” ফেসবুকে সেদিন এ শিরোনাম
একটি লেখার মন্তব্য আমি এভাবে লিখেছিলাম- “এই ছেলে তোকে কি বলে ডাকি
বলতো? কুকুর, বিড়াল, শুকর? না এ নামে তোকে ডাকলে পশুজাতীর যে আর মান
ইজ্জত রইবে না। ডাকা ডাকি বাদ দিই। বরং তোর মায়ের মতই তোর জন্য দোয়া করি-
“তুই বেঁচে থাক বছরের পর বছর অনন্তকাল”। খোদার কাছে প্রার্থনা এই যে,
তিনি যেন তোর অমানুষী মনে উপলব্ধি সৃষ্টি না করে তোর কাছে আজ্রাইল না
পাঠান। চিঠি পড়ে তোর মায়ে কষ্ট আমি পুরটা উপলব্ধি করতে পারছি না। এতো
বেশী কষ্ট উপলব্ধি করি কি করে? তোর জন্য ফরিয়াদ করি, খোদা যেন তোকে তোর
মায়ের মত সমকষ্ট দিয়ে পৃথিবী ত্যাগ করান। এর বেশী কষ্ট তোর জন্য বোধ করি
প্রয়োজন পড়বে না। তোর মা কষ্ট যেমনটা পেয়েছেন ঠিক তেমন কষ্টই তোকে দিক
খোদা। ভালো থাকিস.. ”। ফেসবুকে আমার এ মন্তব্যের পর এর সমর্থনে শতাধিক
মন্তব্য পেয়েছি যা পরলে অনেকেরই চোখে জল আসবে।
বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানো ঐ মা তার ছেলেকে লিখেছেন-“খোকা তুই কেমন আছিসরে? বউমা
আর আমাদের ছোটো দাদুভাই সবাই ভালো আছে তো? জানি তোদের তিন জনের ছোট
সংসারে প্রত্যেকেরই খুব কাজ। তবুও তোদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ। একদিন
একটু সময় করে এই বুড়ি মাকে দেখতে আয় না! কিরে, আসবি না? ওঃ বুঝতে পেরেছি!
এখনো আমার উপর থেকে অভিমান যায়নি বুঝি! আমাকে যেদিন বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানোর
ব্যবস্থা করেছিলি, সেদিন ঝগড়া করেছিলাম বৃদ্ধাশ্রম থেকে আমাকে নিতে আসা
লোকজনদের সঙ্গে। জানি শেষ দিনটাতে একটু বেশি রকমেরই বাড়াবাড়ি করে
ফেলেছিলাম, তাছাড়া আর কিইবা আমি করব বল, সময় মতো ওরা এসে আমার জিনিসপত্র
সব জোর করে গাড়িতে উঠিয়ে নিল, তারপর বারবার তাগাদা দিতে লাগল। বাবা কারণ
আমি তোর সঙ্গে দেখা করে আসার জন্য তাদের কাছে সময় চেয়েছিলাম, তারা সময়
দিলেও শেষ পযর্ঞ্চন্ত তুই আসিসনি। তুই কাজে এত ব্যস্ত থাকিস তখন আমার মনে
ছিলনা। পরে মনে পড়েছিল, তাই তোর সঙ্গে দেখা না করেই চলে এসেছি। তুই রাগ
করিসনি তো? আর সেদিন আমার সেই জেদ দেখে বউমা তো রেগেই আগুন। তাছাড়া তার
তো রাগবারই কথা! আমাকে নিয়ে যেতে যারা এসেছিলো, অল কিছুক্ষণের মধ্যেই
তারা যা তড়িঘড়ি শুরু করে দিলৃতা দেখবার জন্য পাশের বাড়ি থেকে কেউ কেউ
উঁকি দিতে লাগলো। এতো বউমার একটু লজ্জাবোধ হবেই। সেদিন তোদের যে অপমান
করে এসেছি তোরা সেসব ভুলে যাস কেমন করে! আমার কথা ভাবিস না। আমি খুব ভালো
আছি! আর কেনই-বা ভালো থাকবনা বল? তোরা তো আমার ভালো থাকবারই বন্দোবস্ত
করে দিয়েছিস। তবে একটা কথা, আমার কথা যদি তোর কখনো-কোনোদিন মনে পড়ে; তখন
যেন নিজেকে তুই শেষ করে দিস না। তুই এখনো একশ বছর বেঁচে থাক।”
বৃদ্ধাশ্রম অবহেলিত বৃদ্ধদের জন্য শেষ আশ্রয়। তাঁদের সারা জীবনের অবদানের
যথার্থ স¡ীকৃতি, শেষ সময়ের সম্মান ও নিরাপত্তা দেয়া হয় এসব বৃদ্ধাশ্রমে।
এখানে তাঁরা নির্ভাবনায়, সম্মানের সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে বাকি দিনগুলো
কাটাতে পারেন। প্রয়োজনে অনেক বৃদ্ধাশ্রমে চিকিৎসারও সুন্দর ব্যবস্থা করা
আছে। কিন্তু সকল প্রাপ্তির মাঝেও এখানে যা পাওয়া যায় না তা হলো নিজের
পরিবারের সান্নিধ্য। বৃদ্ধ বয়সে মানুষ তার সনত্মান, নাতি-নাতনিদের সঙ্গে
একত্রে থাকতে চান। তাদের সঙ্গে জীবনের আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতে চান।
সারাজীবনের কর্মব্যস্ত সময়ের পর অবসরে তাদের একমাত্র অবলম্বন এই
আনন্দটুকুই। বলা যায় এর জন্যই মানুষ সমগ্র জীবন অপেক্ষা করে থাকে।
বৃদ্ধাশ্রমে আশ্রয় পাওয়া যায়, সঙ্গীসাথী পাওয়া যায়, বিনোদন পাওয়া যায়,
কিন্ত শেষ জীবনের এই পরম আরাধ্য আনন্দটুকু পাওয়া যায় না যাঁর জন্য তারা
এই সময়টাতে প্রবল মানসিক যন্ত্রণা আর ভারাক্রানত্ম হৃদয়ে আবেগাপস্নুত হয়ে
ওঠেন।নেহায়েত অনন্যপায় হয়ে, ইচ্ছার বাইরে যাঁরা বাবা- মাকে বৃদ্ধাশ্রমে
পাঠান, তাঁদের কথা ভিন্ন। কিন্তু যাঁরা নিজের পর্যাপ্ত সম্পদ ও সময় সুযোগ
থাকার পরও শুধু অবহেলা করে পিতা-মাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিয়ে ভুলে
যান, তাঁদের স্মরণ রাখা দরকার, এমন সময় তাঁদের জীবনেও আসতে পারে। যে
বাবা-মা একসময় নিজে না খেয়েও সনত্মানকে মুখে তুলে খাইয়ে দিতেন, তাঁরা আজ
কোথায় কেমন আছেন সেই খবর নেয়ার সময় যাঁর নেই তাঁর নিজের সনত্মানও হয়ত
একদিন তাঁর সঙ্গে এমনই আচরণ করবে। বিভিন্ন উৎসবে, যেমন ঈদের দিনেও যখন
তারা তাদের সনত্মানদের কাছে পান না, সনত্মানের কাছ থেকে একটি ফোনও পান
না, তখন অনেকেই নীরবে অশ্রম্নপাত করেন আর দীর্ঘশ¡াস ছাড়েন। এমনকি সেই
সনত্মানকে অভিশাপ দিয়ে কামনা করেন, তাঁর সনত্মান তাঁর সঙ্গে যে আচরণ করল,
ভবিষ্যতে তাঁর ছেলের সনত্মানও যেন একই আচরণ করে।
একদিন যে সন্তানের জন্য বাবা-মা ছিলেন স্নেহময়, যে সন্তান একটু আঘাত
পেলেই বাবা হয়ে উঠতেন চিন্তিত। যে সন্তানকে নিজে হাত দিয়ে খাইয়ে দিয়েছেন,
কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছেন এবং কখনই নিজের অসুবিধার কথা সন্তানদের বুঝতে
দেননি। আজকাল সমাজে এমন কিছু সন্তান দেখা যায়, যারা কি না মা-বাবার এতোসব
আদর-যত্নের কথা ভুলে মা-বাবাকে ঠেলে দেয় অজানা গন্তব্যে। বৃদ্ধ ও অসহায় বলে তাদের ঠিকানা হয় বৃদ্ধাশ্রমে। ঘরের মধ্যে সবার থাকার জায়গা হলেও এখানে বৃদ্ধ মা-বাবার জায়গা হয় না। আসলে একজন মা-বাবা তার সন্তানদের জন্য যা করেন, তা তাদের পক্ষে সারা জীবনেও শোধ করা সম্ভব নয়। বুড়ো বয়সে এসে তারা চায় একটু শান্তি, ভালোবাসা ও স্নেহ। এ বয়সে একটু আদর-যত্ন পেলেই তারা খুশি হন। মা-বাবা চান সন্তানরা যেন তার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনে।
আমাদের মনে রাখা উচিত আজ যিনি সন্তান, তিনিই আগামী দিনের পিতা কিংবা মা। বৃদ্ধ বয়সে এসে মা-বাবারা যেহেতু শিশুদের মতো কোমলমতি হয়ে যায়, তাই তাদের জন্য সুন্দর জীবনযাত্রার পরিবেশ তৈরি করাই সন্তানের কর্তব্য। আর যেন কখনো কোনো পতা-মাতার ঠিকানা বৃদ্ধাশ্রম না হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। তাদের জন্য তৈরি করতে হবে একটা নিরাপদ ও সুন্দর পৃথিবী।
আসলে মা-বাবা তার সন্তানদের জন্য যা করেন, তা তাদের পক্ষে সারা জীবনেও
শোধ করা সম্ভব নয়। বুড়ো বয়সে এসে তারা চান একটু শান্তি, ভালোবাসা ও স্নেহ। এ বয়সে একটু আদর-যত্ন পেলেই তারা খুশি হন। মা-বাবা চান সন্তানরা যেন তার কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনে। আমাদের মনে রাখা উচিত, আজ যিনি
সন্তান, তিনিই আগামী দিনের পিতা কিংবা মা। বৃদ্ধ বয়সে এসে মা-বাবারা যেহেতু শিশুদের মতো কোমলমতি হয়ে যায়, তাই তাদের জন্য সুন্দর জীবনযাত্রার
পরিবেশ তৈরি করাই সন্তানের কর্তব্য। আর যেন কখনো কোনো পিতা-মাতার ঠিকানা বৃদ্ধাশ্রম না হয়, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। তাদের জন্য তৈরি করতে
হবে একটা নিরাপদ ও সুন্দর পৃথিবী।
লেখক : মহা সচিব- “কলামিস্ট ফোরাম অফ বাংলাদেশ“।