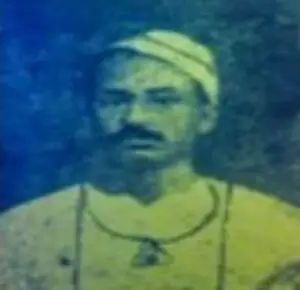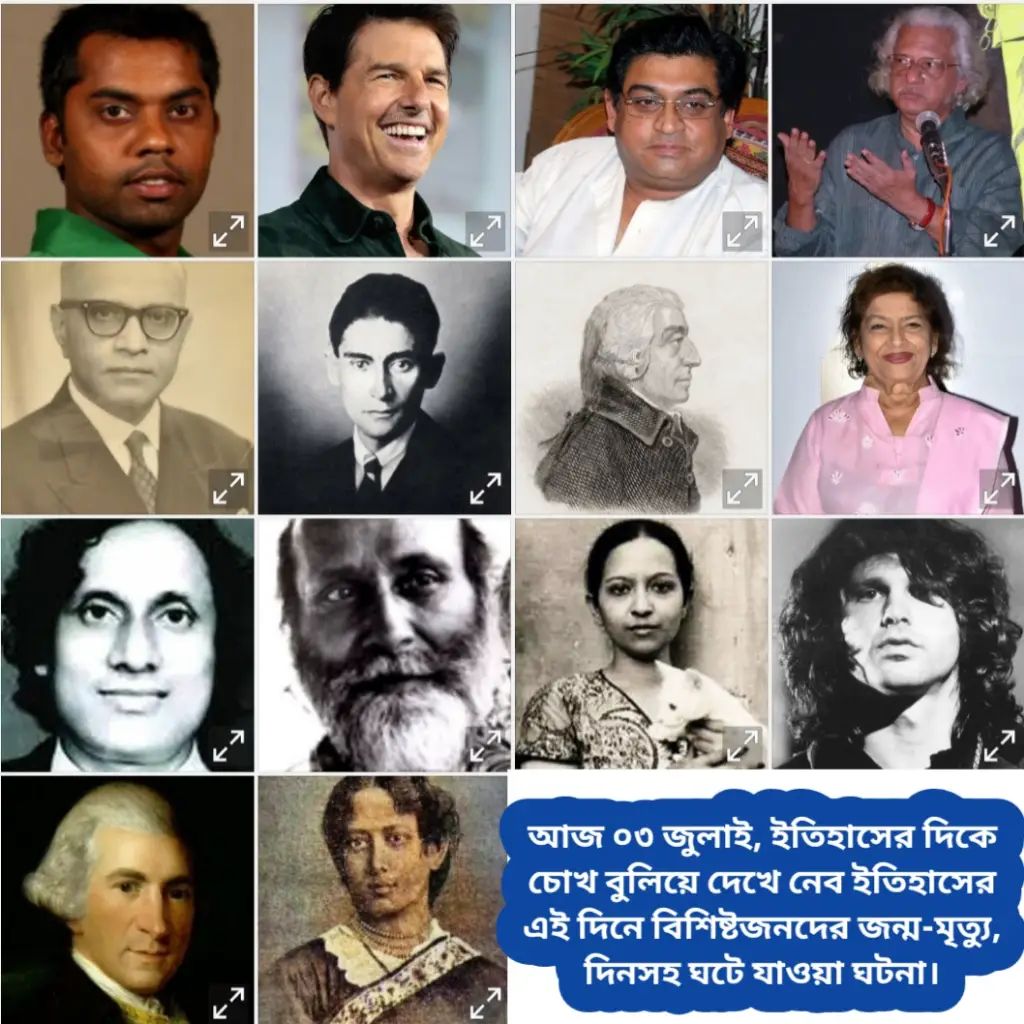স্বামী বিবেকানন্দ শুধু বাঙালির জীবনের এক আদর্শ মহামানবই নন, তিনি যুগাবতার । তিনি ছিলেন একজন হিন্দু সন্ন্যাসী, দার্শনিক, লেখক, সংগীতজ্ঞ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় অতীন্দ্রিয়বাদী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের একমাত্র শিষ্য । তাঁর দেখানো আদর্শের রাস্তা যুক্তিবোধের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় মানুষকে।
আধ্যত্মকে এক অন্য পর্যায়ে উন্নত করে বিবেকানন্দ সকলের জীবনকে আরও বেশি করে আলোর দিকে ঠেলে দিয়েছেন । স্বামী বিবেকানন্দ জীবপ্রেমের দীক্ষা পান শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে, যেখানে তিনি বলেছেন ‘যত্র জীব, তত্র শিব’। জীবের সেবা করলে স্রষ্টারও সেবা করা হয় । স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ । সবার আগে মানব সেবা । সুতরাং মানুষের সেবার মাধ্যমে ঈশ্বরের সেবা করা সম্ভব। জীবপ্রেমের দর্শন প্রকাশ পেয়েছে তাঁর দুটি চমৎকার লাইনেঃ
“বহুরুপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবপ্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর ।”
তাই আমরা কেউ বিবেকানন্দকে পরিপূর্ণভাবে বুঝিনি । কারণ তিনি ছিলেন বহুমাত্রিক ব্যক্তিত্ব । তিনি প্রচুর বই পড়তেন । দর্শন, ধর্ম, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, শিল্পকলা, সাহিত্য, ইত্যাদি বিষয়ে । তা ছাড়া তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল বেদ, উপনিষদ, ভাগবতগীতা, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, প্রভূতি হিন্দু ধর্ম গ্রন্থে । যার জন্য সংগীত, চিত্রকলা, দর্শন, রাষ্ট্রনীতি, ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজতত্ব, ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর ছিলো গভীর ব্যুৎপত্তি । তাই তিনি নিজেই বলেছেন, “বিবেকানন্দকে বুঝতে হলে আরেক বিবেকানন্দকে দরকার” । কর্মী বিবেকানন্দ, সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, গুরু বিবেকানন্দ, শিষ্য বিবেকানন্দ, জ্ঞানী বিবেকানন্দ, যোগী বিবেকানন্দ, কবি বিবেকানন্দ সবই বাহ্য । কারণ এই সমস্ত গুণেই তিনি শীর্ষস্থানের অধিকারী হলেও তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয়, ‘ভালোবাসায় ভরা হৃদয় বিবেকানন্দ’ ।
বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের “শিব জ্ঞানে জীব সেবা” মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন । তাই তিনি মানুষের কল্যাণ সাধনকেই প্রকৃত ঈশ্বর সাধনা বলে মনে করেছিলেন ।
বিবেকানন্দ ছিলেন মানব প্রেমিক সন্ন্যাসী । মানুষের কল্যাণের জন্য তিনি ধর্ম ও বিজ্ঞান উভয়কেই সমানভাবে প্রয়োজন বলে মনে করেছিলেন । তাঁর মতে “ধর্ম”” মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বকে ফোটাবে । বিজ্ঞান মানুষকে সুখ ও সমৃদ্ধি উপহার দেবে । শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ প্রথমে আত্মবিশ্বাসী হবে । আর আত্মবিশ্বাস থেকে আসবে আত্মনির্ভরশীলতা । বিবেকানন্দের মতে, শিক্ষাই সমাজের সকল সমস্যা দূরীকরণের মূল চাবি কাঠি । শিক্ষার আলো মানুষের মনের অন্ধকারকে দূর করে এবং মানুষকে স্বনির্ভর করতে সাহায্য করে । বিবেকানন্দের শিক্ষা পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যেই ছিল সমাজে যথার্থ “মানুষ” তৈরি করা -যাতে চরিত্র গঠিত হয়, মনের শক্তি বাড়ে । বুদ্ধি বিকশিত হয়, মানুষ নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে শেখে । উপরন্ত বিবেকানন্দের শিক্ষা ছিল সার্বজনীন । তিনি চেয়েছিলেন বিশেষভাবে যুব সমাজের নবচেতনার অভ্যুদয় । নিষ্ঠা, সততা ও আত্মনির্ভরতা ছিল তাঁর আরাধ্য । এসব গুণ জগতের সব সমাজের সব মানুষেরই সম্পদ ।

( ২ )
এখানে বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য – বিবেকানন্দ যেভাবে ভারতবর্ষকে চিনেছিলেন বা অনুভব করেছিলেন, অন্য কোনো ব্যক্তি ঠিক সেভাবে ভারতবর্ষকে অনুভব করতে পারেননি । পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করে বিবেকানন্দ ধন্য মনে করেছিলেন । ভগিনী নিবেদিতার ভাষায়, “তিনি নিজেই হয়ে উঠেছিলেন ভারতবর্ষ – রক্তমাংসে গড়া ভারত প্রতিমা ।” আর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ রোমাঁ রোলাঁকে (ফরাসী সাহিত্যিক) বলেছিলেন, “যদি ভারতবর্ষকে জানতে চাও বিবেকানন্দকে জানো । বিবেকানন্দের লেখা আগে পড়ো । ”
বিবেকানন্দ সহজে ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেবকে গুরু মানেননি । প্রথমদিকে নরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবকে গুরু বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলেন । এমনকি তাঁর চিন্তাভাবনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রকাশ করেছিলেন । অথচ উল্টে তিনি রামকৃষ্ণ দেবের ব্যক্তিত্বের কাছে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন । যার জন্য ঘনঘন তিনি দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু করেন । ব্রাহ্ম সমাজের সদস্য নরেন্দ্রনাথ সেইসময় মূর্তিপূজা, বহুদেববাদ, রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কালী পুজা সমর্থন করতেন না । এমনকি অদ্বৈত বেদান্তমতবাদকেও তিনি ঈশ্বরদ্রোহিতা ও পাগলামি বলে উড়িয়ে দিতেন । নরেন্দ্রনাথ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবকে পরীক্ষা করতেন । রামকৃষ্ণ দেবও শান্তভাবে তার যুক্তি শুনে বলতেন, “সত্যকে সকল দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করবি ।”
১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের গলায় ক্যান্সার ধরা পড়ে । চিকিৎসার প্রয়োজনে তাঁকে প্রথমে উত্তর কলকাতার শ্যামপুকুর ও পরে কাশীপুরের একটি বাগান বাড়িতে স্থানান্তরিত করা হয় । সেখানেই নরেন্দ্র নাথের ধর্ম শিক্ষা চলতে থাকে । কাশীপুরে নরেন্দ্রনাথ নির্বিকল্প সমাধি লাভ করেন । তারপর রামকৃষ্ণ দেবের কাছ থেকে সন্ন্যাস ও গৈরিক বস্ত্র লাভ করেন । রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব নরেন্দ্রনাথকে শিক্ষা দেন “মানব সেবাই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সাধনা” । এরপর ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট শেষ রাত্রে কাশীপুরেই রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব প্রয়াত হন । ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নরেন্দ্রনাথের গুরুভ্রাতা বাবুরামের মা নরেন্দ্রনাথ ও অন্যান্য সন্ন্যাসীদের আঁটপুরে আমন্ত্রণ জানান । সেখানেই তাঁরা রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের মতো জীবন যাপনের সিদ্ধান্ত নেন । তখন নরেন্দ্রনাথ “স্বামী বিবেকানন্দ” নাম গ্রহণ করেন ।
এরপরে পরিব্রাজকরূপে তাঁকে আমরা কী দেখলাম । ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে পরিব্রাজকরূপে মঠ ত্যাগ করেন বিবেকানন্দ । পরিব্রাজক হিন্দু সন্ন্যাসীর এক ধর্মীয় জীবন — এই জীবনে তিনি স্বাধীনভাবে পর্যটন করে বেড়ান কোনো স্থায়ী বাসস্থান ও বন্ধন ছাড়াই । পরিব্রাজক জীবনে বিবেকানন্দের সঙ্গী ছল একটি কমন্ডলু, লাঠি এবং তাঁর প্রিয় দুটি গ্রন্থ -ভাগবদ্গীতা ও ইশানুসরণ । বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় ও সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে সুপরিচিত হন । এই সময় ভিক্ষোপজীবী হয়ে সারা ভারত পদব্রজেই পর্যটন করেন বিবেকানন্দ । সেইজন্য বিবেকানন্দকে সারা বিশ্বের মানুষ “পরিব্রাজক” হিসেবে জানে । ভারতবর্ষ পর্যটনের সময় তিনি বিভিন্ন পণ্ডিত, দেওয়ান, রাজা এবং হিন্দু-মুসলমান, খ্রিষ্টান এমনকি নিম্নবর্গীয় ও সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গেও মেলামেশা ও একসঙ্গে বাস করেন ।

( ৩ )
১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বারাণসী থেকে যাত্রা শুরু করেন । তখন সাক্ষাৎ হয় বিশিষ্ট বাঙালী লেখক ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বিশিষ্ট সন্ত ত্রৈলঙ্গস্বামীর সাথে । বৃন্দাবন, হথরাস ও হৃষীকেশে ভ্রমণের সময় হথরাসে তাঁর সঙ্গে স্টেশন মাস্টার শরৎচন্দ্র গুপ্তের সাক্ষাত হয় । তিনি পরে বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সদানন্দ নামে পরিচিত হন । তিনি ছিলেন বিবেকানন্দের প্রথম যুগের শিষ্য । ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দে আবার নৈনিতাল, আলমোড়া, দেরাদুন, ঋষীকেশ, হরিদ্বার এবং হিমালয় ভ্রমণে যান । তারপর রওনা দেন দিল্লি । এইভাবে পশ্চিম ভারত, দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ সারেন ।
১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে ৩০শে জুন থেকে ১৪ই জুলাই শিকাগো যাওয়ার পথে বিবেকানন্দ জাপান ভ্রমণ করেন । তিনি ঘুরে দেখেছিলেন কোবে, ওসাকা, কিওটো, টোকিও আর য়োকোহামা শহর । ১০ই জুলাই ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দে য়োকোহামার ওরিয়েন্টাল হোটেল থেকে তাঁর ভক্ত মাদ্রাজের আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লেখা চিঠিতে বিবেকানন্দ জানিয়েছিলেন জাপান নিয়ে তাঁর মুগ্ধতার কথা । তিনি জাপানীদের “পৃথিবীর সবচেয়ে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন জনগণের অন্যতম” বলে অভিহিত করেছিলেন । তারপর চিন, কানাডা হয়ে তিনি শিকাগো শহরে পৌঁছান ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দের জুলাই মাসে । কিন্তু শিকাগো শহরে পৌঁছে মূলত দুটি সমস্যায় পড়েন । মহাসভা শুরু হতে দেড় মাস বাকী । অন্যটা কোনো খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠানের প্রশংসাপত্র বা পরিচয়পত্র ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তিকে প্রতিনিধি হিসাবে বিশ্বধর্ম মহাসভায় গ্রহণ করা হবে না । তারপর তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন হেনরি রাইটের সংস্পর্শে এলেন । তাঁকে হার্ভার্ডে আমন্ত্রণ জানানোর পর এবং ধর্মসভায় বক্তব্যদানে বিবেকানন্দের প্রশংসাপত্র না থাকা প্রসঙ্গে রাইটের বক্তব্য, “আপনার কাছে প্রশংসাপত্র চাওয়াটা হচ্ছে স্বর্গে সূর্যের আলো দেওয়ার অধিকার চাওয়ার মতো অবস্থা ।” রাইট তখন প্রতিনিধিদের দায়িত্বপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের নিকট এক চিঠিতে লিখলেন, “আমাদের সকল অধ্যাপক একত্রে যতটা শিক্ষিত ইনি তাঁদের থেকেও বেশী শিক্ষিত ।”
বিশ্বধর্ম মহাসভা ১৮৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর শিকাগোর আর্ট ইনস্টিটিউটে উদ্বোধন হয় । তিনি ভারত এবং হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেন । পাশ্চাত্যে অভিযানের নিরিখে যেসব অভিজ্ঞতা, তাতে শিকাগো বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে উপস্থিত হয়ে ভারতীয় সনাতন ও বেদান্তের উপর ভাষণ দেওয়া ভীষন তাৎপর্যপূর্ণ । তাঁর বক্তব্য শুরু করলেন, “আমেরিকার ভ্রাতা ও ভগিনীগণ …।” — সম্ভাষন করে । তাঁর বক্তব্যে সহিষ্ণুতা ও মহাজাগতিক গ্রহণযোগ্যতা প্রসঙ্গ ওঠে । গীতা থেকে উদাহরণমূলক পংক্তি তুলে ধরেন । তাঁর বক্তব্যে বিশ্বজনীন চেতনা ধ্বনিত হয় ।
প্রেসের কাছে তিনি “ভারতের সাইক্লোন সন্ন্যাসী” হিসেবে অভিহিত হন । “নিউ ইয়র্ক ক্রিটিক” লিখেছিল “ঐশ্বরিক অধিকারবলে তিনি একজন বক্তা এবং তাঁর শক্তিশালী, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারার চেয়ে বরং আগ্রহোদ্দিপক ছিল ঐ সকল ছন্দময়ভাবে উচ্চারিত শব্দসমূহ ।” আমেরিকার পত্রিকাসমূহ বিবেকানন্দকে “ধর্মসভার সবচেয়ে মহান ব্যক্তিত্ব” হিসেবে প্রতিবেদন লিখেছিল । পরবর্তীতে শ্রীমতি অ্যানি বেসান্ত ভারতে ফিরে এসে লিখেছিলেন, “গেরুয়াধারী কম বয়স্ক প্রতিনিধি হিসেবে বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলন মঞ্চে বিবেকানন্দ ছিলেন সূর্যের মতো তেজস্বী এক পুরুষ ।”
তারপর ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর আমেরিকা ও ইংল্যান্ড ভ্রমণ শেষে ইংল্যান্ড থেকে ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা দেন । তারপর ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী কলম্বো তিনি পৌঁছান ।

( ৪ )
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই বিবেকানন্দের সদর্থক ভূমিকা । রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের একনিষ্ঠ ভক্ত সুভাষ চন্দ্র বসু । সেই বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেন, বিবেকানন্দ ছিলেন “আধুনিক ভারতের স্রষ্টা ।” জাতীয়তাবাদ নিয়ে বিবেকানন্দের চিন্তাভাবনার প্রতি তিনি ছিলেন সতত সংবেদনশীল । সুতরাং বিবেকানন্দের স্বদেশমন্ত্র দেশ স্বাধীনতার প্রেক্ষাপটে বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ । বলা চলে বিবেকানন্দ স্বাধীনতা আন্দোলনকে প্রভাবিত করেছিলেন । যার জন্য মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন, “বিবেকানন্দের রচনা তাঁর “দেশপ্রেম হাজারগুণ” বৃদ্ধি করেছিল ।” যখন পরাধীন ভারতবাসী আত্মশক্তি হারিয়ে ফেলেছিল, তখন বিবেকানন্দ চেয়েছেন মানুষের আত্মশক্তির বিকাশ । তাই তিনি বলেছেন, “তোমরা ঈশ্বরের সন্তান, অমৃতের অধিকারি, পবিত্র ও পূর্ণ । তুমি নিজেকে দুর্বল বলো কী করে ? ওঠো, সাহসী হও, বীর্যবান হও ।”
স্বদেশমন্ত্রে তিনি বলেছেন, হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা … এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করবে ? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে ? হে ভারত, ভুলিও না তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী । ভুলিও না, তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর । ভুলিও না, তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের —নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে । ভুলিও না, তুমি জন্ম হতেই “মায়ের” জন্য বলিপ্রদত্ত । ভুলিও না, নীচজাতি, মুর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই । হে বীর, সাহস অবলম্বন করো, সদর্পে বলো —- আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই । বলো, মুর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চন্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই । সদর্পে বলো, ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী । বলো ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ । ভারতের কল্যান, আমার কল্যান । ”
১৯০২ খ্রিষ্টাব্দের ৪ই জুলায় রাত ৯.১০ মিনিটে ধ্যানরত অবস্থায় দেহত্যাগ করেন । তাঁকে বেলুড়ে গঙ্গা নদীর তীরে একটি চন্দন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া চিতার উপর দাহ করা হয় । যার বিপরীত পাশে ষোলো বছর আগে রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের মরদেহ দাহ করা হয়েছিল ।
আজ তাঁর শুভ জন্মদিন (জন্মঃ ১২ই জানুয়ারী, ১৮৬৩) । তাঁর শুভ জন্মদিনে আমার শতকোটি প্রণাম ।
কলমে : দিলীপ রায়।
———–০————–