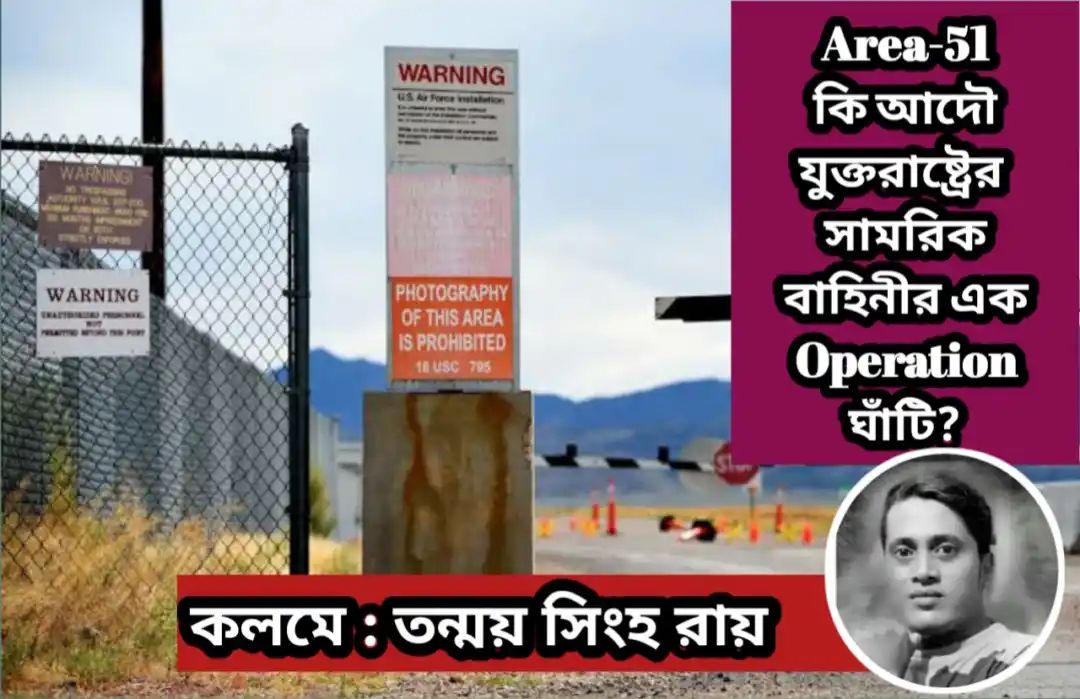জাহাজ ও দু-দুটো ট্রেন পাল্টে অবশেষে ৩০ শে জুলাই রাত ১১ টায় তিনি উপস্থিত হলেন শিকাগোয়।
ক্লান্ত, অবসন্ন শরীরটা সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশে তাকে ফেলেছে এক চরম অস্বস্তিজনক পরিস্থিতিতে, এমনটাই মনে হচ্ছিল। পরিস্থিতি ধারণ করলো আরো জটিল আকার যখন তিনি জানতে পারলেন যে, ধর্মমহাসভায় পরিচয় পত্র আবশ্যক ও যোগদানের তারিখ-ও পেরিয়ে গেছে।
মুহুর্তের মধ্যেই মনে হতে লাগলো অতি যত্নে সাজানো সমস্ত রঙীন স্বপ্নগুলো তাঁর চোখের সামনেই হয়ে যাচ্ছে টুকরো টুকরো!
এদিকে শিকাগোর মতন বড়লোকি শহরে থাকার খরচ।
সামান্য পুঁজি ফুরিয়ে আসার মুহুর্তে তিনি আবিষ্কার করলেন বস্টন নামক একটি শহর যেখানে থাকা-খাওয়ার খরচ অনেকাংশে কম। অবশেষে বস্টন অভিমুখে রওনাকালীন ট্রেনে পরিচয় হয় ক্যাথেরিন স্যানবর্ন নামক এক ধনী ও প্রভাবশালী মহিলার সাথে।
প্রতিভাদীপ্ত সুদর্শন এক পুরুষের সাথে তিনি নিজেই এসে পরিচয় করে দু-এক কথায় মুগ্ধ হয়ে স্বামীজি-কে তার বাড়িতে থাকার জন্যে জানালেন হার্দিক আমন্ত্রণ!
এ অবস্থায় স্বামীজি সাদরে গ্রহণ করলেন সে আমন্ত্রণ। ক্যাথেরিন স্যানবর্নের বাড়িতে থাকাকালীন স্বামীজি তাঁর এক শিষ্যকে চিঠিতে জানালেন, ‘এখানে থাকায় আমার প্রতিদিনের এক পাউন্ড করে বেঁচে যাচ্ছে আর তাঁর(ক্যাথেরিন স্যানবর্ন) প্রাপ্তি হল, তিনি তাঁর বন্ধুদের আমন্ত্রণ করে দেখাচ্ছেন ভারতের এক বিচিত্র জীবকে!’
বস্টনে থাকাকালীন ক্যাথেরিন স্যানবর্নের সূত্রে সেখানকার শিক্ষিত সমাজে স্বামীজি হয়ে উঠেছিলেন ভীষণভাবে পরিচিত। অকস্মাৎ ক্যাথেরিনের মাধ্যমে স্বামীজির পরিচয় হয় হাভার্ড ইউনিভার্সিটির এমন একজন সুবিখ্যাত প্রফেসার জন হেনরি রাইটের সাথে যাকে বলা হত বিশ্বকোষতুল্য জ্ঞানভান্ডারের অধিকারী। কিন্তু স্বামীজির তেজোদীপ্ত প্রতিভার আলোক ছটায় বিষ্ময়ে হতবাক হলেন তিনিও। পরিচয়পত্র না থাকায় তিনি (স্বামীজি) মহাধর্মসম্মেলনে যোগ না দিতে পারার সংক্ষিপ্ত কারণ বিশ্লেষণে প্রফেসার প্রত্যুত্তর করলেন, ‘মহাশয়, আপনার কাছে পরিচয়-পত্র চাওয়ার অর্থ এমন যে সূর্যকে প্রশ্ন করা যে তার কিরণ দেওয়ার অধিকার আছে কিনা।’ অতঃপর মহাধর্মসম্মেলনের এক কর্মকর্তার উদ্দেশ্যে প্রফেসার রাইট লিখলেন :
‘ইনি (স্বামীজি) এমন একজন ব্যক্তি যে, আমেরিকার সমস্ত প্রফেসারের পান্ডিত্য এক করলেও এঁর পান্ডিত্যের সমান হবে না।’ অবশেষে স্বামীজী’র মনে হতে লাগলো তাঁর রঙীন স্বপ্নগুলো জোড়া লাগতে শুরু হল আবার ধীরে ধীরে।
বস্টনে সপ্তা তিনেক থাকার পর শেষে তিনি রওনা হলেন শিকাগো অভিমুখে।
১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩, শিকাগোর কলম্বাস হলে সকাল দশটায় বিশ্ব ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা ভূমিষ্ঠ হয়েছিল যে আধিদৈবিক সিংহপুরুষের দ্বিতীয় অধিবেশনের ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে তিনি-ই হলেন স্বামী বিবেকানন্দ।
“সিস্টার্স এন্ড ব্রাদার্স অফ অ্যামেরিকা”…… হাজার হাজার দর্শকমণ্ডলীর হর্ষধ্বনি ও করতালিতে ফেটে পড়েছিলো মঞ্চ।
মনে হচ্ছিল এক সংক্ষিপ্ত শক্তিশালী আঁধি সেই মুহুর্তে, সেই স্থানের উপস্থিতজনেদের উপর দিয়ে বয়ে গেলো। কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের জয়ঢাক তিনি বাজাননি। মহা ধর্মসম্মেলনে যেখানে সবাই নিজ নিজ ধর্ম সম্বন্ধেই বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেখানে স্বামীজি দেখিয়েছিলেন, সব ধর্মই সত্য কারণ প্রতিটি ধর্মই মানুষকে পৌঁছে দেয় একই সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে।
১৯৯২ সালে স্বামীজির শিকাগো বক্তৃতার একশত বছর পূর্তির আগে এলেনর স্টার্ক নামক এক আমেরিকান মহিলা স্বামীজিকে নিয়ে ‘দ্য গিফট আন-ওপেন্ড.. এ নিউ আমেরিকান রেভলিউশন’ নামক একটি বই লিখেছিলেন যাতে লেখিকা স্বামীজির বাণীকে বর্ণনা করেছেন ‘উপহার’ বলে অর্থাৎ, ভারতবর্ষ থেকে আমেরিকাকে দেওয়া উপহার।
তিনি বলেছেন, সেই উপহারের প্যাকেট আমেরিকা খুলে দেখেনি, স্বামীজির বাণীকে তারা জীবনে ব্যবহার করেনি। যদি তারা তা করত, একটা নতুন ধরণের বিপ্লব ঘটে যেত আমেরিকাবাসীদের জীবনে।’ ঐ বইতেই তিনি উল্লেখ করেছেন, ‘কলম্বাস আবিষ্কার করেছিলেন আমেরিকা মহাদেশের ভূখন্ডটা কিন্তু বিবেকানন্দ আবিষ্কার করেছিলেন আমেরিকার আত্মাকে!’
‘আমি মুসলমানের মসজিদে যাব, খৃষ্টানদের গির্জায় প্রবেশ করে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর সামনে নতজানু হব, বৌদ্ধদের বিহারে প্রবেশ করে আমি বুদ্ধের শরণাপন্ন হব আবার অরণ্যে প্রবেশ করে হিন্দুদের পাশে বসে ধ্যানমগ্ন হব…. শুধু তাই নয়, ভবিষ্যতে যে সব ধর্ম আসতে পারে, তাদের জন্যেও আমার হৃদয় আমি উন্মুক্ত রাখবো।’ (স্বামীজির বাণী) ।
কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আজ একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও আমরা স্বল্প শিক্ষিত ও সীমিত জ্ঞানীরা চুড়ান্ত সাম্প্রদায়িক, আত্মকেন্দ্রিক ও চরম ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা বইছে আমাদের রক্তে। তাঁর আদর্শের পরমানুটুকুও ক্রমশঃ আমাদের শরীর থেকে হতে চলেছে নিশ্চিহ্ন!
শরীরের লজ্জা আমরা সহজেই ঢাকতে পারি পোষাক দিয়ে কিন্তু মনুষ্যত্বের এ লজ্জা আমরা ঢাকবো কোন পোষাকে??
( তথ্য সংগৃহীত)