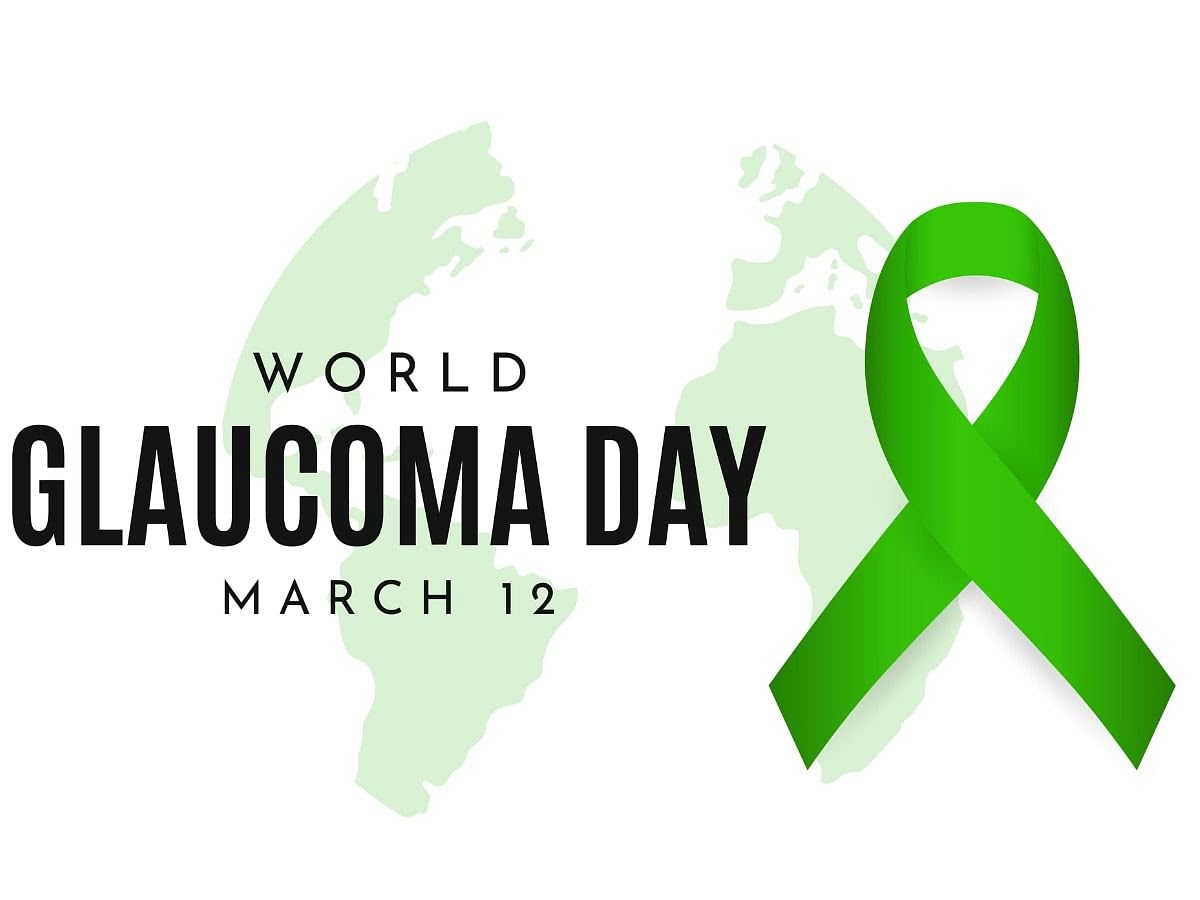সমরেশ মজুমদার একজন ভারতীয় বাঙালি কথাসাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক। শহরকেন্দ্রিক জীবনের আলেখ্য বারবার উঠে এসেছে তার লেখায়। যে কারণে তাকে আপাদমস্তক ‘আরবান’ লেখক বলে অনেক সময় বর্ণনা করা হয়।
প্রাথমিক জীবন এবং শিক্ষা—–
সমরেশ মজুমদার ১৯৪২ সালের ১০ই মার্চ পশ্চিমবঙ্গের গয়েরকাটায় জন্মগ্রহণ করেন।পিতা কৃষ্ণদাস মজুমদার ও মাতা শ্যামলী দেবী। তার শৈশব কেটেছে ডুয়ার্সের গয়েরকাটা চা বাগানে। ভবানী মাস্টারের পাঠশালায় তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। এরপর বিদ্যালয়ের পাঠ জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলে । তিনি কলকাতায় আসেন ১৯৬০ সালে। বাংলায় স্নাতক সম্পন্ন করেন কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে।
সাহিত্য চর্চা—–
কর্মজীবনে তিনি আনন্দবাজার পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে যুক্ত ছিলেন। গ্রুপ থিয়েটারের প্রতি তার ছিল প্রবল অনুরাগ। তাঁর প্রথম গল্প “অন্যমাত্র” একটি মঞ্চ নাটক হিসাবে রচিত হয়েছিল এবং সেখান থেকেই লেখক হিসাবে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়েছিল। তাঁর লেখার আরেকটি সংস্করণ 1967 সালে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সমরেশ মজুমদারের প্রথম উপন্যাস “দৌড়” 1975 সালে দেশে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি তাঁর লেখা গল্প বা উপন্যাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি; ছোটগল্প, ভ্রমণকাহিনী থেকে শুরু করে গোয়েন্দা গল্প পর্যন্ত, তিনি কিশোর উপন্যাস লেখায় প্রবল। তার প্রতিটি উপন্যাসের বিষয়বস্তু ভিন্ন, লেখার গতি ও গল্প বলার ধরন পাঠকদের নাড়া দেয়। চা বাগানের মাদেশিয়া সমাজ থেকে কলকাতার নিম্নবিত্ত মানুষ রক্তমাংসে তার কলমে এসেছে।
গ্রন্থ তালিকা——
সমরেশ মজুমদারের উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলির মধ্যে ভিক্টোরিয়ার বাগান, আট কুঠুরি নয় দরজা, অনুরাগ, সাতকাহন, তেরো পার্বণ, স্বপ্নের বাজার, উজান, গঙ্গা,ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তার ট্রিলজি ‘উত্তরাধিকার, কালবেলা, কালপুরুষ’ বাংলা সাহিত্য জগতে তাকে বিশেষ খ্যাতির অধিকারী করেছে।
জলছবির সিংহ, মেয়েরা যেমন হয়, একশো পঞ্চাশ (গল্প সংকলন), ভালবাসা থেকে যায়, নিকট কথা, ডানায় রোদের গন্ধ, উত্তরাধিকার, কালবেলা, কালপুরুষ, সত্যমেব জয়তে, আকাশ না পাতাল, তেরো পার্বণ, সওয়ার, টাকাপয়সা, তীর্থযাত্রী, কলিকাল, স্বপ্নের বাজার, কলকাতা, অনুরাগ, তিনসঙ্গী, ভিক্টোরিয়ার বাগান, সহজপুর কতদূর, অনি, সিনেমাওয়ালা, গর্ভধারিণী, হৃদয় আছে যার, সর্বনাশের নেশায়, ছায়া পূর্বগামিনী, এখনও সময় আছে, স্বনামধন্য, আমাকে চাই, উজান গঙ্গা, কষ্ট কষ্ট সুখ, কুলকুণ্ডলিনী, কেউ কেউ একা, জনযাজক, সূর্য ঢলে গেলে, আশ্চর্যকথা হয়ে গেছে, অগ্নিরথ, অনেকই একা, আট কুঠুরি নয় দরজা, আত্মীয়স্বজন, আবাস, জলের নিচে প্রথম প্রেম, জ্যোৎস্নায় বর্ষার মেঘ, দায়বন্ধন, দিন যায় রাত যায়, দৌড়, বড় পাপ হে (গল্প), বিনিসুতোয়, মনের মতো মন, মেঘ ছিল বৃষ্টিও, শরণাগত, শ্রদ্ধাঞ্জলি, সাতকাহন, সুধারানী ও নবীন সন্ন্যাসী, হরিণবাড়ি, কইতে কথা বাধে, মধ্যরাতের রাখাল, আকাশে হেলান দিয়ে, কালোচিতার ফটোগ্রাফ, আকাশকুসুম, অহংকার, শয়তানের চোখ, হৃদয়বতী, স্বরভঙ্গ, ঐশ্বর্য, আকাশের আড়ালে আকাশ, কালাপাহাড়, সন্ধেবেলার মানুষ, বুনোহাঁসের পালক, জালবন্দী, মোহিনী, সিংহবাহিনী, বন্দীনিবাস, মৌষলকাল, মানুষের মা, গঙ্গা, বাসভূমি, লক্ষ্মীর পাঁচালি, শেষের খুব কাছে, জীবন যৌবন, আহরণ, বাসভূমি, এত রক্ত কেন, এই আমি রেণু, উনিশ বিশ।
পুরস্কার ও সম্মাননা——
আনন্দ পুরস্কার -১৯৮২; বাংলা চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি পুরস্কার, দিশারী ও চলচিত্র প্রসার সমিতি – শ্রেষ্ঠ স্ক্রিপ্ট রাইটার – ১৯৮২; সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার, ১৯৮৪; বঙ্কিম পুরস্কার – ২০০৯; বঙ্গবিভূষণ – ২০১৮, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত। চিত্রনাট্য লেখক হিসাবে জয় করেছেন বিএফজেএ, দিশারী এবং চলচ্চিত্র প্রসার সমিতির এওয়ার্ড। সমরেশ কলকাতা ও বাংলাদেশএর সর্বকালের অন্যতম সেরা লেখক হিসাবে পাঠকমন জয় করেছেন।
মৃত্যু—–
২০২৩ সালের ২৫ই এপ্রিল মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ জনিত সমস্যার কারণে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখানেই ৮ই মে তিনি প্রয়াত হন।
।। তথ্য : সংগৃহীত উইকিপিডিয়া ও বিভিন্ন ওয়েবসাইট।।