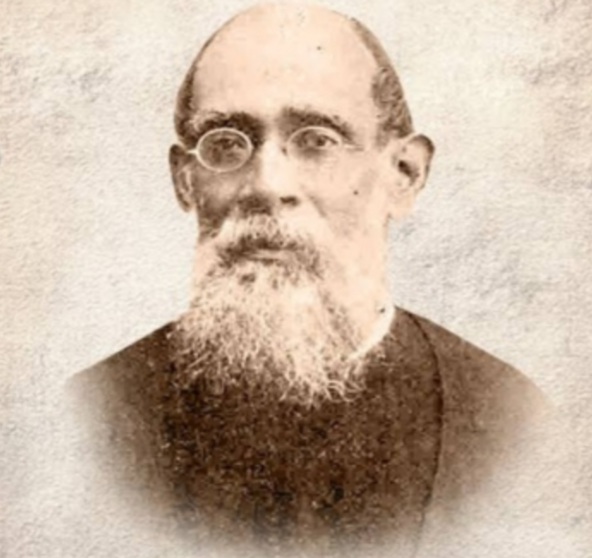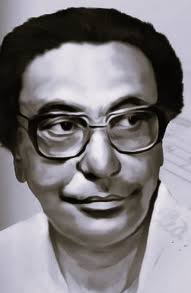10 আগস্ট কার্বন নিঃসরণ কমাতে এবং টেকসই শক্তির প্রচারের বৈশ্বিক প্রচেষ্টায় একটি উল্লেখযোগ্য দিন চিহ্নিত করে – আন্তর্জাতিক জৈব-জ্বালানি দিবস। এই দিনটি প্রথম জৈব-জ্বালানী ফ্লাইটের বার্ষিকীকে স্মরণ করে, যা 10 আগস্ট, 2018-এ হয়েছিল। বিশ্ব যখন জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করছে, তখন জৈব-জ্বালানি স্বল্প-কার্বনে রূপান্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। অর্থনীতি
জৈব জ্বালানী কি?
জৈব-জ্বালানি হল জৈব পদার্থ, যেমন উদ্ভিদ, শেওলা বা কৃষি বর্জ্য থেকে উৎপাদিত জ্বালানি। তারা জীবাশ্ম জ্বালানির একটি ক্লিনার বিকল্প অফার করে, গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন এবং অ-নবায়নযোগ্য সম্পদের উপর নির্ভরতা হ্রাস করে। জৈব-জ্বালানি পরিবহন, গরম করা এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য তরল জ্বালানি সহ বিভিন্ন রূপে ব্যবহার করা যেতে পারে।
জৈব-জ্বালানির ইতিহাস
জৈব-জ্বালানির ধারণাটি 20 শতকের গোড়ার দিকে, কিন্তু এটি 1970 এর দশকে তেল নিষেধাজ্ঞার সাথে গতি লাভ করে। তখন থেকে, গবেষণা ও উন্নয়ন জৈব-জ্বালানি উৎপাদন, দক্ষতা এবং সামর্থ্যের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির দিকে পরিচালিত করেছে।
জৈব-জ্বালানির প্রকারভেদ
1. প্রথম প্রজন্মের জৈব জ্বালানি: ভুট্টা, আখ এবং সয়াবিনের মতো খাদ্য শস্য থেকে উৎপাদিত।
2. দ্বিতীয় প্রজন্মের জৈব-জ্বালানি: কৃষি বর্জ্য, শেওলা এবং সুইচগ্রাস জাতীয় খাদ্যবহির্ভূত জৈববস্তু থেকে উদ্ভূত।
3. তৃতীয় প্রজন্মের জৈব-জ্বালানি: ব্যাকটেরিয়া এবং ইস্টের মতো অণুজীব থেকে উৎপন্ন।
জৈব জ্বালানীর উপকারিতা
1. গ্রীনহাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস: জৈব জ্বালানী জীবাশ্ম জ্বালানীর তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম CO2 নির্গত করে।
2. শক্তি নিরাপত্তা: জৈব-জ্বালানি আমদানি করা তেলের উপর নির্ভরতা কমাতে পারে, শক্তির স্বয়ংসম্পূর্ণতা বাড়াতে পারে।
3. গ্রামীণ উন্নয়ন: জৈব-জ্বালানি উৎপাদন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে এবং স্থানীয় অর্থনীতিকে উদ্দীপিত করতে পারে।
4. উন্নত বায়ুর গুণমান: জৈব-জ্বালানি কম দূষক নির্গত করে, বায়ুর গুণমান এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নতি করে।
চ্যালেঞ্জ এবং সুযোগ
1. খরচ এবং পরিমাপযোগ্যতা: জৈব-জ্বালানি উৎপাদন প্রথাগত জ্বালানির তুলনায় বেশি ব্যয়বহুল।
2. ভূমি ব্যবহার এবং খাদ্য নিরাপত্তা: বড় আকারের জৈব-জ্বালানি উৎপাদন জমি এবং সম্পদের জন্য খাদ্য শস্যের সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারে।
3. প্রযুক্তিগত অগ্রগতি: চলমান গবেষণার লক্ষ্য হল দক্ষতা উন্নত করা, খরচ কমানো, এবং নতুন জৈব-জ্বালানি উত্স বিকাশ করা।
বিশ্বব্যাপী উদ্যোগ এবং নীতি
1. পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানী স্ট্যান্ডার্ড (RFS): একটি মার্কিন নীতি যা পরিবহন জ্বালানীতে জৈব-জ্বালানির মিশ্রণ বাধ্যতামূলক করে।
2. ইউরোপীয় ইউনিয়নের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি নির্দেশিকা: পরিবহনে জৈব-জ্বালানি ব্যবহারের লক্ষ্য নির্ধারণ করে।
3. ভারতের জাতীয় জৈব জ্বালানী নীতি: জৈব-জ্বালানি উৎপাদন এবং মিশ্রণ বৃদ্ধির লক্ষ্য।
উপসংহার
আন্তর্জাতিক জৈব-জ্বালানি দিবস টেকসই শক্তি সমাধানের গুরুত্বের অনুস্মারক হিসেবে কাজ করে। যেহেতু বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, জৈব-জ্বালানি জীবাশ্ম জ্বালানির একটি গুরুত্বপূর্ণ বিকল্প প্রস্তাব করে। যদিও চ্যালেঞ্জগুলি অব্যাহত থাকে, চলমান গবেষণা, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি এবং সহায়ক নীতিগুলি এই বাধাগুলি অতিক্রম করতে সাহায্য করতে পারে। জৈব-জ্বালানি গ্রহণ করে, আমরা আমাদের কার্বন পদচিহ্ন কমাতে পারি, শক্তি নিরাপত্তা উন্নত করতে পারি এবং আরও টেকসই ভবিষ্যত তৈরি করতে পারি।