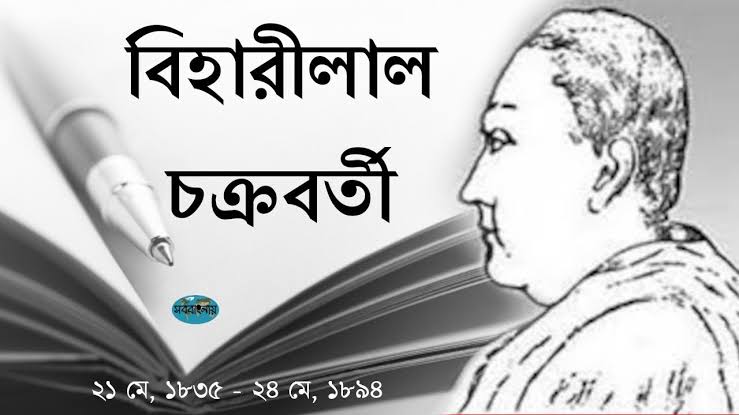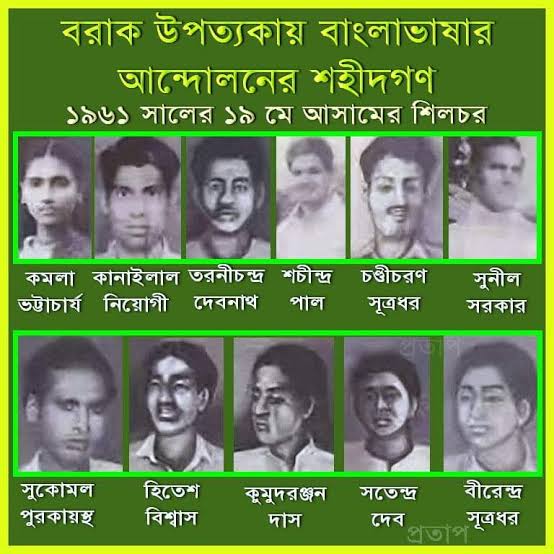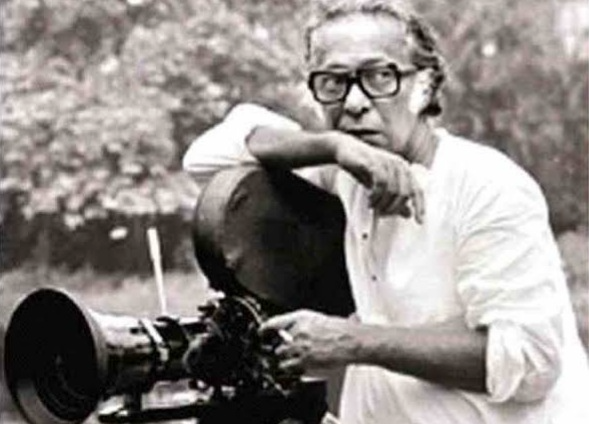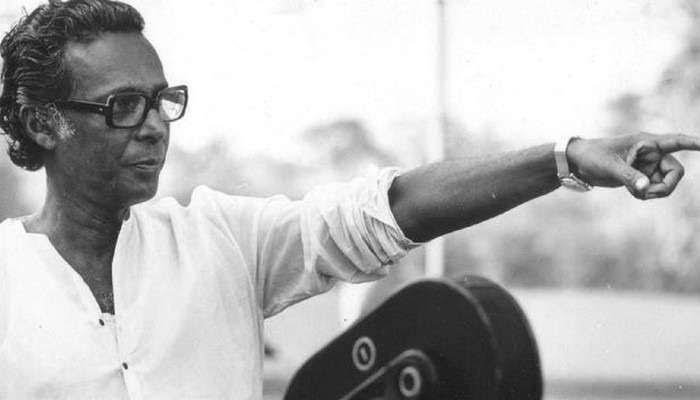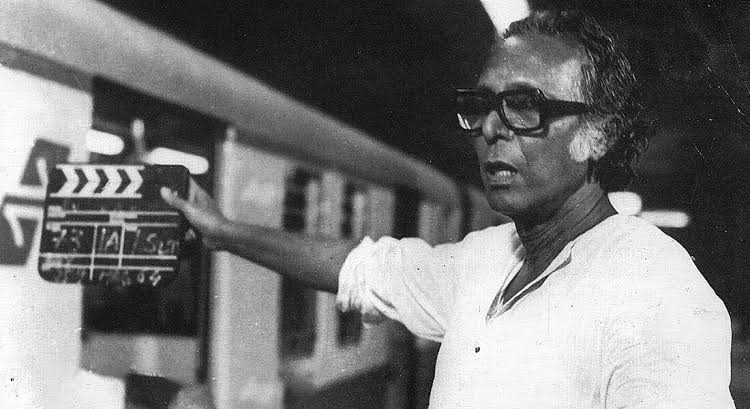১৮৯৯ সালের ২৪ মে কবি নজরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেন অবিভক্ত ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গের চুরুলিয়া গ্রামে। আর যখন ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে দ্বিখণ্ডিত হয়, তখন বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের বয়স মাত্র ৪৮ বছর দুই মাস ৯ দিন ।
কবি নজরুল ইসলামের কাব্যজীবন ,সাহিত্য ও গান তাঁর সৃষ্টি বিশ্লেষণে দেখা যায় কবি নজরুল ইসলামকে দলগত কিংবা ব্যক্তিগতভাবে কখনোই বিদ্রোহী বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে কবি নজরুল ইসলাম কোন রাজনৈতিক দলের ছিলেন না বা বিদ্রোহী দলও গঠন করেননি বা কোনো বিদ্রোহী সন্ত্রাসী দলে যোগদানও করেন নাই।
তৎকালীন সময়ে কবির সবচেয়ে নিকটের বন্ধু ছিলেন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতা কমরেড মুজফর আহম্মেদ। কবি তাঁর সংস্পর্শে থেকেও কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন নাই।
কবিকে আত্মাভিমানী বললে ভুল বা কখনোই অত্যুক্তি হবে না, যদি বা কবি নজরুল তাত্ত্বিক বা দার্শনিক হিসেবে গণ্য নন, কিন্তু তাঁর সাম্যবাদী, ঈশ্বর, মানুষ, পাপ, বারাঙ্গনা, নারী, কুলি-মজুর প্রভৃতি কবিতায় সুস্পষ্টভাবে অভেদ মানবতত্ত্ব এবং সাম্যবাদী চৈতন্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। এসব ক্ষেত্রে তাঁর মানবিক সংশোধনের প্রাচুর্যই বেশি চোখে পড়ে।
কবির নান্দনিক কাব্যিক শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁর অভিমান ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে , দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্যের কারণে।
তাই বোধকরি তাকে বিদ্রোহ কবি বলে গণ্য করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর রচনাসমগ্র বিশ্লেষণ করলে চোখে পড়ে যে,তিনি একাধারে বিদ্রোহের উন্মাদনা তৎসঙ্গে অন্যধারে প্রেমের অবাধ্য আকুতি।
এই পরস্পরবিরোধী দ্বৈত অবস্থানের চৌম্বিকতায় একপর্যায়ে লক্ষ্যণীয় সৃষ্টি কবি নজরুলের ‘বিদ্রোহী’ কবিতা..যেমন,
আমি চির দুর্দ্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস,
মহা প্রলয়ের আমি নটরাজ,
আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস!…আমি দুর্বার ,
আমি ভেঙে করি সব চুরমার।
আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল,
আমি দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়মকানুন শৃঙ্খল!
আমি মানি নাকো কোন আইন…
বৃটিশরাজের আমলাতান্ত্রিক ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় রাজা-প্রজার এতই ব্যবধান যে সাধারণত রাজার সম্মান ছিল ঈশ্বরেরই সমকক্ষ তৎসঙ্গে রাজকর্মচারীরা নিজেদেরকে রাজার প্রতিভূ অর্থাৎ জনগণের তথা প্রজার প্রভু বলে মনে করত নিজেদের আর তাদের আচার-আচরণও ছিল রাজন্যবর্গসুলভ। নজরুল এই অবস্থানকে কটাক্ষ করে লিখেছেন সেই কথাগুলো এবং উপসংহারে ঘোষণা করেছিলেন ,–
গণতন্ত্রের জয়,বন্ধু, এমনি হয়-
জনগণ হ’ল যুদ্ধে বিজয়ী,রাজার গাহিল জয়!
প্রজারা যোগায় খোরাক- পোশাক,
কি বিচার বলিহারি,
প্রজার কর্মচারী নন তাঁরা রাজার কর্মচারী!
মোদেরি বেতনভোগী চাকরেরে সালাম করিব মোরা,
ওরে পাবলিক সার্ভেন্টদের আয় দেখে যাবি তোরা!..
এরপর নজরুল আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেছিলেন,-
“-এ আশা মোদের দুরাশাও নয়,সেদিন সুদূরও নয়,
সমবেত রাজ-কণ্ঠে যেদিন শুনিব প্রজার জয়।”
কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন মূলত বিদ্রোহী কবি। তার বিদ্রোহ ছিল সমাজ ও রাষ্ট্রের সব অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে। আর সেই বিদ্রোহকে কেন্দ্র করেই তার স্বাধীনচেতা হৃদয়ের আগুন প্রজ্বলিত হয়েছিল আপন পরাধীন দেশের স্বাধীনতা কামনায়। এমন সরাসরি স্বাধীনতার প্রবক্তা হওয়া সেই আমলে আর কোনো কবির পক্ষে সেকালে সম্ভব হয়নি। কারণ, প্রভু ইংরেজরা অসন্তুষ্ট হবেন এমন কোনো কথা উচ্চারণ করার।
অথচ সেই সময় বিশের দশকে কবি নজরুল ইসলাম ধূমকেতু পত্রিকা বের করেছেন তখন সংবাদপত্রে “স্বাধীনতা”র কথা বলা রীতিমতো ছিল ঝুঁকিপূর্ণ। সেখানে কংগ্রেসের জাঁদরেল নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে অটোনমি বা স্বায়ত্তশাসন আর সেলফ গভর্নমেন্টের কথা বললেন, ঋষি অরবিন্দও তাই বলেছিলেন, আর স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীও বলেছিলেন।
অথচ ১৯২১ সালের শেষ সপ্তাহে আহমেদাবাদে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনে প্রখ্যাত ঊর্দু কবি ফজলুল হাসান হসরৎ মোহানী তার বক্তব্যে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি করেছিলেন।
১৯২২ সালের ১৩ অক্টোবর নজরুল ইসলামের সম্পাদিত ধূমকেতু পত্রিকার ১ম বর্ষ ১৩শ সংখ্যায় “ধূমকেতুর পথ” প্রবন্ধে সেদিন লিখেছিলেন,
–“সর্বপ্রথম ধূমকেতু পত্রিকাতেই ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চাওয়া হয়েছিল। লিখেছিলেন, —
“স্বরাজ টরাজ বুঝি না, কেননা ও কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশির অধীনে থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা ও শাসনভার সমস্তই থাকবে ভারতীয়দের হাতে। তাতে কোনো বিদেশি মোড়লীর অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। যারা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এদেশে মোড়লী করে দেশকে শ্মশান ভূমিতে পরিণত করেছেন তাদের পাততাড়ি গুটিয়ে বোঁচকা পুটুলি বেঁধে সাগর পাড়ে পাড়ি দিতে হবে। প্রার্থনা বা আবেদন-নিবেদন করলে শুনবো না। তাদের অতটুকু সুবুদ্ধি হয়নি এখনো যে, আমাদের এই প্রার্থনা করার, ভিক্ষে করার কুবুদ্ধিটুকুকে ওদের দূর করতে হবে।”
সেইসময় সংবাদপত্রে এমন দুঃসাহসিক স্বাধীনতা ঘোষণার কথা উচ্চারণ, বোধ করি ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।
নজরুল ইসলামের লড়াই ছিল সমাজে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার সর্বাত্মক প্রচেষ্টায়।তাই কবির সাহিত্যে সকল বঞ্চিত ব্যথিত মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে ছিল আপসহীন সংগ্রামে অধিকার সমন্বিত।
নজরুল ইসলাম নিঃস্বার্থ সাম্যবাদের আলো জ্বালিয়ে জগতকে আলোকিত করতে চেয়েছিলেন।
কবি নজরুল ছিলেন জ্ঞানবান সাম্যবাদী মানুষ যার লড়াই ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অসাম্যের বিরুদ্ধে, অবিচারের বিরুদ্ধে এবং সর্বোপরি অত্যাচারীর বিরুদ্ধে যেখানে মানুষের জ্ঞানালোকিত স্বাধীনতা থাকবে অবাধ ও পক্ষপাত বিবর্জিত। যেখানে অন্যায়ের কণাটুকুও ঠাঁই পাবে না মনুষ্যত্বের আধারে। নজরুলের সাম্যে ধর্ম-বর্ণ শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থায় সব মানুষ সমান, যেখানে অর্থনৈতিক বৈষম্য নেই, যেখানে ধর্মের ব্যবধান নেই, কোনো বিভেদ নেই বর্ণের…
“গাহি সাম্যের গান
বুকে বুকে হেথা তাজা সুখ ফোটে,
মুখে মুখে তাজা প্রাণ।
বন্ধু এখানে রাজা-প্রজা নাই, নাই দরিদ্র ধনী,
হেথা পায় নাকো’ কেহ খুদ ঘাঁটা,কেহ দুধ-সর-ননী।
ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের প্রেক্ষাপটে তিনি সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে ভারতের দুই বৃহৎ ধর্মীয় সম্প্রদায় তথা হিন্দু ও মুসলমান যদি একতাবদ্ধ হয়ে একদেহে একই স্বার্থে স্বাধীনতার লড়াই চালিয়ে যেতে সক্ষম হয় তাহলে বৈরী অমানবিক শক্তি নস্যাৎ হতে বাধ্য। তাই তিনি গান বেঁধেছিলেন ,–
“কাণ্ডারী হুঁশিয়ার”
দুর্গম গিরি কান্তার-মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি-নিশীতে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার।
এখানে আরো লিখেছেন–
“হিন্দু না ওরা মুসলিম?” ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?
কাণ্ডরী! বল, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা’র।”
বিদেশি শত্রুর মোকাবেলা করতে হলে চাই জাতির ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম। তাই স্বাধীনতার পক্ষে কবি নজরুল ইসলাম চেয়েছিলেন, সমগ্র জাতি তথা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ঐকান্তিক মিলন।
১৯২৬ সালের এপ্রিল মাসে কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে নজরুল সামরিক কায়দায় যে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলেন তাদের সমবেত কণ্ঠে উদ্বোধনী সঙ্গীতও ছিল এই “কান্ডারী হুঁশিয়ার”।
আজ আমরা সাম্যের গান শুধুই মুখে গাই বলি। হৃদয় থেকে গাই না …!!
গাহি সাম্যের গান
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই,
নহে কিছু মহীয়ান।
নাই দেশ-কাল পাত্রের ভেদ,
অভেদ ধর্ম জাতি;
সব দেশে, সব কালে,
ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।
সব শেষে আবারো বলি আমাদের সুমতি হোক্ আমরা আমাদের জীবনে কবি নজরুলের সত্য-সুন্দর , সাম্য আদর্শকে উপজীব্য করে বাঁচতে শিখি, মানুষকে ভালোবাসতে শিখি আর মানুষের অধিকারকে লুণ্ঠিত লাঞ্ছিত না করে যথার্থ সম্মান করতে শিখি । তবেই আমরা যেমন গৌরবান্বিত হবো, তেমনি প্রকৃত শ্রদ্ধাজ্ঞাপনও করা হবে কবির প্রতি …