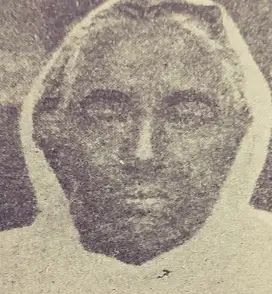ভূমিকা
মানবসভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে পরিবার সমাজের মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে। পরিবারের গঠন, পরিচালনা, মূল্যবোধ সংরক্ষণ এবং প্রজন্মের পর প্রজন্মে সংস্কৃতি ও নৈতিকতার বাহক হিসেবে পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আর এই পরিবারের কেন্দ্রবিন্দুতে যে ব্যক্তি সবচেয়ে নিবিড়ভাবে যুক্ত থাকেন, তিনি একজন নারী। নারী শুধু পরিবারের সদস্য নন, তিনি এর প্রাণ, ভারসাম্য, দিকনির্দেশনা ও আবেগী স্তম্ভ।
অতীতের ঐতিহ্য থেকে বর্তমানের গতিশীল সামাজিক বাস্তবতায় নারীর ভূমিকা বিস্তৃত হয়েছে, রূপান্তরিত হয়েছে, আবার অনেক ক্ষেত্রে গভীর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখিও হয়েছে। একসময় পরিবার বলতেই বোঝাত গৃহস্থালি কাজের চেনা দৃশ্য—নারী যেন পরিবার পরিচালনার একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু সময় বদলেছে। নারীর শিক্ষা, কর্মসংস্থান, আর্থিক স্বাধীনতা, সামাজিক সচেতনতা ও অধিকারপ্রাপ্তি পরিবারে তার ভূমিকা পুনর্নির্ধারণ করেছে।
এই প্রবন্ধে পরিবারে নারীর ভূমিকার ঐতিহাসিক বহুমাত্রিক দিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতা, আধুনিক যুগের নতুন বাস্তবতা, চ্যালেঞ্জ, এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে গভীর আলোকপাত করা হয়েছে।
—
১. ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট
১.১ প্রাচীন সমাজে নারীর অবস্থান
ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে নারী কখনো দেবী, কখনো শ্রমিক, কখনো বঞ্চিত, কখনো সমাজের কেন্দ্রীয় শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার সংস্কৃতিতে নারীকে শক্তুি বা শক্তির প্রতীক হিসেবে দেখা হলেও বাস্তব জীবনে তাকে গৃহবন্দী ও নির্ভরশীল করে রাখার প্রবণতা ছিল প্রবল।
প্রাচীন কৃষিনির্ভর সমাজে নারীরা মূলত গৃহকর্ম, সন্তান প্রতিপালন, খাদ্য সংরক্ষণ এবং পরিবার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করতেন। পুরুষরা বাহিরের কাজ করতেন, আর নারী গৃহের অভিভাবক হিসেবে অবস্থান করতেন। নারীর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তা প্রকাশ্য বা সামাজিক স্বীকৃতি ততটা পায়নি।
১.২ মধ্যযুগে নারীর ভূমিকা
মধ্যযুগে ধর্মীয়, সামাজিক এবং রাজনৈতিক কাঠামোগুলো নারীর চলার পথকে আরও সীমাবদ্ধ করলেও পরিবারে তাদের গুরুত্ব কমেনি। পরিবারে নারী ছিলেন শৃঙ্খলা, নৈতিকতা ও ঐতিহ্য রক্ষার প্রধান বাহক। সন্তানদের শিক্ষাদীক্ষা, পরিবারের মূল্যবোধ গঠন তাদের হাতেই নির্ভর করত। তবে সেই মূল্যায়ন ছিল “গৃহস্থালী”র সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ।
১.৩ উপনিবেশকাল ও নারীশিক্ষার উত্থান
উপনিবেশ ও সংস্কার আন্দোলনের যুগে নারীশিক্ষার প্রসার ঘটে। রামমোহন রায়, ইশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরদের প্রচেষ্টায় নারীরা শিক্ষার আলো পেতে শুরু করেন। এতে নারীর চিন্তাধারায়, আত্মবিশ্বাসে নতুন মাত্রা যোগ হয় যা পরিবারে তাদের দায়িত্বের পাশাপাশি পরামর্শদাতা ও সিদ্ধান্তগ্রহণকারীর ভূমিকাও বাড়িয়ে দেয়।
—
২. পরিবারে নারীর বহুমাত্রিক ভূমিকা
নারীর দায়িত্ব শুধু একটি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়; পরিবারে তার উপস্থিতি আকাশের মতো বিস্তৃত। নিচে পরিবারে নারীর প্রধান কিছু ভূমিকা তুলে ধরা হলো।
২.১ গৃহিণী হিসেবে ভূমিকা
গৃহিণীর দায়িত্ব মানবসভ্যতার প্রাচীনতম ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। রান্না, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, পরিবারের সদস্যদের সুস্থতা, অর্থব্যয়ের হিসাব রাখা—এই সবই দীর্ঘদিন ধরে নারীর ওপর বর্তেছে।
অনেকে এটিকে ‘অসম্মানজনক’ কাজ ভাবলেও বাস্তবে এ সব দায়িত্ব পরিবার পরিচালনার ভিত্তি। একজন দক্ষ গৃহিণী পুরো পরিবারের জীবনযাপনকে সহজ, সুন্দর ও সুস্থ রাখেন। সমাজে গৃহিণীর শ্রম অদৃশ্য হলেও এর গুরুত্ব অপরিসীম।
২.২ মা হিসেবে ভূমিকা
মায়ের ভূমিকা পরিবারে সবচেয়ে আবেগী, তবু সবচেয়ে দায়িত্বপূর্ণ। সন্তানের শারীরিক পরিচর্যা ছাড়াও নৈতিকতা, সহমর্মিতা, সামাজিক বোধ, ভাষা, মূল্যবোধ—সব প্রথম শেখানো হয় মায়ের কাছেই।
একজন মা শুধু সন্তান জন্ম দেন না; তিনি গড়ে তোলেন ভবিষ্যৎ মানুষ। তাই পরিবারে নারীর এই ভূমিকা অন্য যে কোনো দায়িত্বের চেয়ে বিস্তৃত।
২.৩ স্ত্রী হিসেবে সহযাত্রী
পরিবারের স্থিতিশীলতার অন্যতম শর্ত হলো দাম্পত্যজীবনের ভারসাম্য। স্ত্রী হিসেবে নারী শুধু আবেগী সমর্থনই দেন না, তিনি পরিবারের অর্থনীতি, সন্তান শিক্ষা, সামাজিক সম্পর্ক, আত্মীয়তা—সবকিছুর সাথে যুক্ত হয়ে থাকেন।
আধুনিক যুগে দাম্পত্য সম্পর্ক আর কর্তৃত্বের নয়, বরং অংশীদারিত্বের। নারী-পুরুষ উভয়েই সমানভাবে সিদ্ধান্ত নেন, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করেন, দায়িত্ব ভাগ করে নেন।
২.৪ পরিবারের ‘সংস্কৃতির ধারক’ হিসেবে নারী
পরিবারের রীতি, নীতি, প্রথা, উৎসব, ভাষা—সবকিছুই নারী প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে এগিয়ে দেন।
তিনি শেখান—
কীভাবে অতিথিকে আপ্যায়ন করতে হয়
কোন উৎসবে কোন খাবার রান্না হয়
কিভাবে বড়দের সম্মান করতে হয়
সামাজিক আচরণ কেমন হওয়া উচিত
নারী পরিবারকে শুধু চালান না; তিনি পরিবারকে “সংস্কৃতি” দেন।
২.৫ শিক্ষিকা ও দিকনির্দেশক
ছোটো বাচ্চার প্রথম শিক্ষক মা। স্কুল শিক্ষা শুরু হওয়ার আগেই শিশুর মধ্যে—
ভাষাচর্চা
সামাজিক নিয়ম
আত্মবিশ্বাস
আচরণগত বোধ
ধর্মীয় বা নৈতিক মূল্যবোধ
সবকিছু গড়ে ওঠে নারীর মাধ্যমে। একজন শিক্ষিত মা পুরো পরিবারকে প্রভাবিত করেন।
২.৬ কর্মজীবী নারী হিসেবে ভূমিকা
আজকের বিশ্বে নারীর কর্মজীবনের পরিধি বেড়েছে। এখন তিনি—
ব্যাংকার
শিক্ষক
ডাক্তার
প্রকৌশলী
উদ্যোক্তা
সরকারি কর্মকর্তা
রাজনীতিক
হিসেবে সমান সফল।
এর ফলে পরিবারে তার ভূমিকা আরও দৃঢ় হয়েছে। তিনি শুধু গৃহস্থালিই নয়, পরিবারের অর্থনীতিরও অন্যতম ভিত্তি হয়ে উঠেছেন।