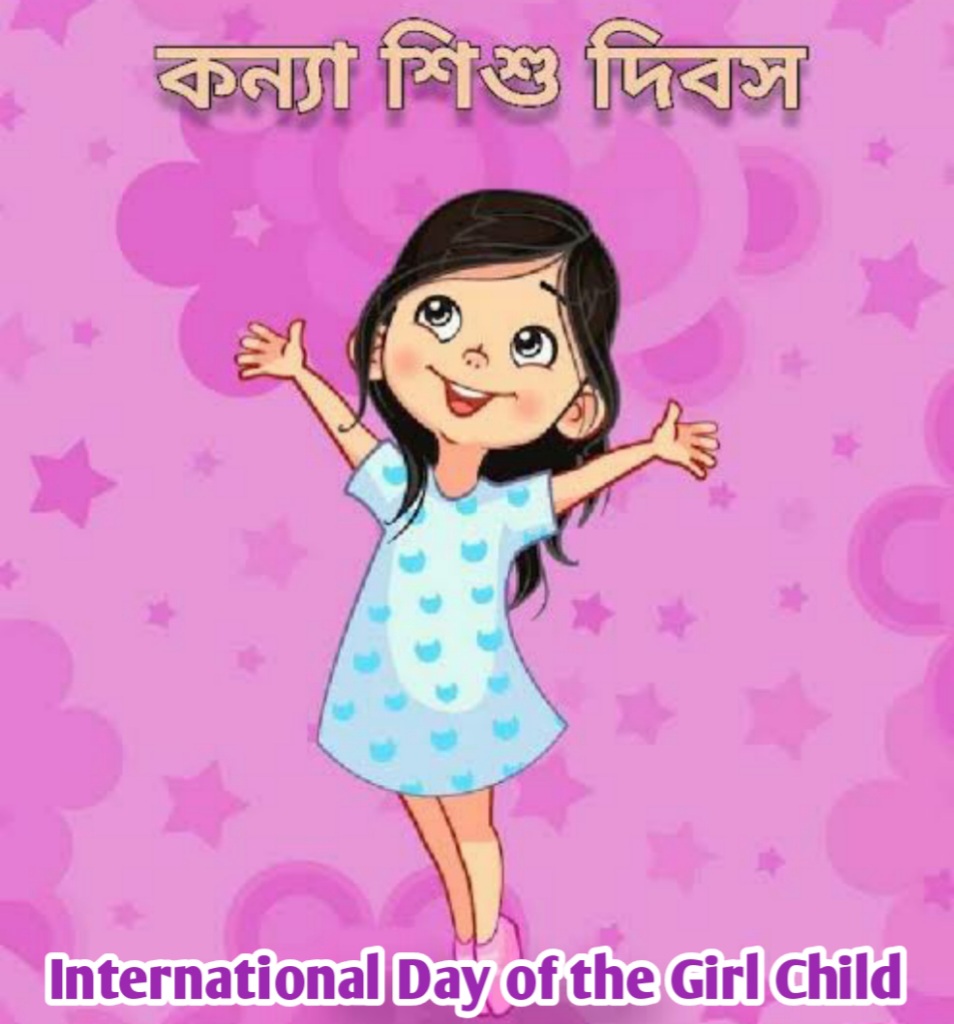‘এই পথ যদি না শেষ হয়, তবে কেমন হত…’ জীবন এক দীর্ঘ্য পথচলা; চড়াই উতরাই এর টুকরো টুকরো অধ্যায় পেরিয়ে স্বপ্ন থেকে সার্থকতার এক দীর্ঘ যাত্রাকথা। সুখ-দুঃখের পরশমাখা এই পথচলা সত্যিই যদি শেষ না হত, তাহলে কেমন হত? যদি অন্তহীন পথে এগিয়ে যেতে পারত জীবন, তাহলে কি হারানোর দুঃখ যন্ত্রণা হারিয়ে যেত চিরকালের মতো?
কিন্তু পথচলা অন্তহীন নয়, হয়ও না। পথের একটা শেষ আছে, পথচলারও। একদিন না একদিন পথের বুকে লেখা হয় জীবনের সমাপ্তি সঙ্গীত। সেই বিষাদ সুরের মূর্ছনায় অশ্রুর আগামীর বুকে জেগে ওঠে শূন্যতার হাহাকার। তখন ইচ্ছে করে বলতে ‘কিছুক্ষণ আরও না হয় রহিতে কাছে’। মনের মাঝে জেগে ওঠে পথ শেষ না হওয়ার দুর্বার আকাঙক্ষা। মন ভাবে যদি পথচলার গল্পকথায় লেখা হত অনন্তের সুর! তাহলে হয়তো খুব ভালো হত। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। হওয়া সম্ভবও নয়। একদিন না একদিন পথ হারিয়ে যায় কোনো এক অজানা রহস্যময় অন্ধকারে। ঠিক তেমনি করে জীবনের পথচলা শেষ করে অজানা অচেনা কোনো আলো আর সুরের জগতে পাড়ি দিয়েছেন সংগীতের এক কিংবদন্তী চরিত্র, সংগীতের স্বর্ণযুগের শেষ প্রতিনিধি গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।
১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের ৪ অক্টোবর কলকাতার ঢাকুরিয়াতে জন্ম সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের। বাবা নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও মা হেমপ্রভা দেবী। পরিবারের তিন পুত্র ও তিন কন্যার মধ্যে সন্ধ্যা ছিলেন সবার ছোটো। তার এক দাদা ও দিদি কম বয়সে মারা গিয়েছিলেন।
বংশ পরম্পরায় সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের পরিবারে গানের পরিবেশ ছিল। তাদের বংশের এক পূর্বপুরুষ রায় বাহাদুর রামগতি মুখোপাধ্যায় নামী সজ্ঞীতজ্ঞ ছিলেন। তার ছেলে সারদাপ্রসাদ গানের চর্চা করতেন। সারদাপ্রসাদের ছেলে ছিলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের দাদু। এরা সকলেই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চর্চা করতেন। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের বাবাও গানবাজনা করতেন। মূলত ভক্তিমূলক গান ছিল তার প্রিয়। পরিবারের সেই গানের ধারা আরও অন্যান্যজনের মতো পেয়েছিলেন সন্ধ্যা। খুব ছোটোবেলা থেকেই তিনি গানের প্রতি আগ্রহী ছিলেন। মেয়ের এই আগ্রহের ব্যাপারটা নজর এড়ায় না তার বাবা-মায়ের। তারাই প্রথম তাকে গানের তালিম দেন। বাবা তাকে ভক্তিমূলক গান শেখাতেন। তার মা নিধুবাবুর টপ্পা খুব ভালো গাইতে পারতেন। অথচ প্রথাগতভাবে গানের শিক্ষা ছিল না তার। মায়ের সুন্দর গান করার দক্ষতা অবাক করত সন্ধ্যাকে যে কথা তিনি তার নিজের আত্মজীবনী ‘গানে মোর কোন ইন্দ্রধনু’ বইতে উল্লেখ করেছেন।
সন্ধ্যার গানের পথচলায় তার দাদা রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বিরাট অবদান রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন তার বোনের গানের গলা অসাধারণ। ঠিকঠাকভাবে যদি তালিম দেওয়া যায় তাহলে সে অনেক দূর যাবে। তিনি তাকে নিয়ে যান যামিনী গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে। তার কাছে ছয় বছর গানের তালিম নেন তিনি। অল্প কিছুদিন চিন্ময় লাহিড়ীর কাছে গান শেখেন।
সন্ধ্যা স্বপ্ন দেখতেন ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলি খানের কাছে গানের তালিম নেওয়ার। নিজের ইচ্ছের কথা ব্যক্ত করেন দাদার কাছে। কিন্তু ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলি খানের কাছে গান শেখার সুযোগ পাওয়া সহজ ছিল না। দাদা তাকে নিয়ে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের কাছে যান। তারই মধ্যস্থতায় স্বপ্ন পূরণ হয় সন্ধ্যার। ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলি খান তাকে গান শেখাতে সম্মত হন। শুরু হয় সন্ধ্যার জীবনের এর স্মরণীয় অধ্যায়।
ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলি খানকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন সন্ধ্যা। তাঁকে ‘বাবা’ বলে সম্বোধন করতেন। তিনিও তাকে নিজের মেয়ের মতো স্নেহ করতেন। গান শেখার জন্য গান গাওয়ার থেকে শোনাটা বেশি জরুরি, এই শিক্ষা তিনি তার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। ওস্তাদ বলতেন, একভাগ গাইতে হবে, তিনভাগ শুনতে হবে। যা সন্ধ্যা অক্ষরে অক্ষরে মানতেন তার জীবনে। ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলি খান মারা গেলে তিনি তাঁর পুত্র মুনাবর আলি খানের কাছে গানের তালিম নেন। পাতিয়ালা ঘরানার গান শেখেন তার কাছে। এছাড়াও গানের তালিম নিয়েছেন সন্তোষকুমার বসু, টি.এ. কানন, চিন্ময় লাহিড়ী প্রমুখদের কাছে।
বারো বছর বয়সে তিনি আকাশবানীতে গল্পদাদুর আসরে গান করেন। এই গানের জন্য পারিশ্রমিক হিসেবে পাঁচ টাকা পেয়েছিলেন। ১৯৪৩ সালে অল বেঙ্গল মিউজিক কনফারেন্স আয়োজিত সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম হন। ১৯৪৬ সালে গীতশ্রী পরীক্ষায় বসেন। সেই সময়ের খ্যাতিমান গায়কেরা ছিলেন এর বিচারক। গীতশ্রী ও ভজন দুই বিভাগেই তিনি প্রথম হন। চোদ্দ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগেই তার গানের প্রথম বেসিক রেকর্ড বের হয়। এইচ.এম.ভি থেকে এই রেকর্ড বের হয়। গীরিন চক্রবর্তীর কথায় ও সুরে রেকর্ডের গান দুটি ছিল ‘তুমি ফিরায়ে দিয়ে যারে’ এবং ‘তোমার আকাশে ঝিলমিল করে’। একটু একটু করে তার নাম ছড়িয়ে পড়তে থাকে।
১৯৪৮ সালে সিনেমায় গান করার সুযোগ পান তিনি। প্রথম ছবি ‘অঞ্জনগড়’। ছবির সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন রাইচাঁদ বড়াল। দ্বিতীয় ছবি রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গীত পরিচালনায় ‘সমাপিকা’ ছবিতে। তবে ‘সমাপিকা’ ছবিটি আগে মুক্তি পায়। এই বছর আরও তিনটি রেকর্ড বের হয় তার। বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের নজরে পড়েন তিনি। ঢাকুরিয়ার এক জলসায় সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গান শুনেছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। তার গান মুগ্ধ করেছিল হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে। ১৯৪৯-এ ‘স্বামী’ ছবিতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুরে তিনি প্রথম গান করেন। গানটি ছিল গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখা – ‘ওরে ঝরা বকুলের দল’। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় বাড়ে বোম্বে আসার পর।
১৯৫০ সালে শচীন দেব বর্মন সন্ধ্যাকে বোম্বে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান তার ছবিতে গান করার জন্য। বোম্বে যাওয়া নিয়ে প্রথমটা একটু দ্বিধায় ছিলেন তিনি। অবশেষে তিনি বোম্বে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। দাদা ও দিদির সঙ্গে বোম্বে যান তিনি। এখানে থাকতেন খার স্টেশনের পাশে এভারগ্রিন হোটেলে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ও তখন বোম্বেতে ছিলেন। তার সঙ্গে সন্ধ্যার পরিচয় বাড়তে থাকে। ১৯৫১-তে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ডুয়েট গান করেন। এস.ডি. বর্মণের সুর দেওয়া গানটি ছিল ‘আ গুপচুপ গুপচুপ পেয়ার করো’। দুজনের সঙ্গীতের জুটির সেই শুরু। তারপর যা হয়েছিল তা ইতিহাস।
যাই হোক, শচীন দেব বর্মণের আমন্ত্রণে বোম্বে গেলেও প্রথম গান করেন অনিল বিশ্বাসের ‘তারানা’ ছবিতে। গানটি ছিল ‘বোল পাপিহে বোল রে/ বোল পাপিহে বোল’ এটি ছিল ডুয়েট গান। তার সঙ্গে গান গেয়েছিলেন সংগীত জগতের আর এক কিংবদন্তী লতা মঙ্গেশকর যিনি তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগেই প্রয়াত হয়েছিলেন। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে লতা মঙ্গেশকরের পরিচয় ও বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। লতা মঙ্গেশকর মাঝে মাঝে তার এভারগ্রিন হোটেলে চলে আসতেন। দুজনে আড্ডা দিতেন। গল্পের পাশাপাশি গান নিয়ে আলোচনা হত। ইতিমধ্যে সন্ধ্যার দিদি কলকাতা ফিরে গেছেন। সেই জায়গায় মা এসেছেন বোম্বেতে, তার সাথে থাকার জন্য। তার মায়ের হাতের রান্না খেতে পছন্দ করতেন লতা মঙ্গেশকর। তিনিও মাঝে মাঝে চলে যেতেন লতাজির বাড়িতে। তার মাও সন্ধ্যাকে খুব পছন্দ করতেন। পরবর্তীকালে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের ঢাকুরিয়ার বাড়িতেও এসেছেন লতা মঙ্গেশকর। দুজনের এই বন্ধুত্ব মৃত্যুর আগে পর্যন্ত অটুট ছিল।
মোট সতেরোটি ছবিতে গান করেছিলেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। কিন্তু নানা কারণে বোম্বেতে থাকতে মন চায় না তার। মাত্র দুবছর পর ফিরে আসেন কলকাতায়। চুটিয়ে গান করতে লাগলেন বাংলা সিনেমায়। পাশাপাশি রেকর্ডের কাজও চলতে থাকে তার। সেই সময় ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ লাইভ সম্প্রচারিত হত। সেখানে গান গেয়েছেন তিনি। ‘মহিষাসুরমর্দিনী’তে তার রেকর্ড করা ‘বিমানে বিমানে আলোকের গানে জাগিল ধ্বনি’ গানটি মানুষের মনে দাগ কাটে।
বাংলা সিনেমার কথা বললে যে জুটির কথা অবশ্যই করে বলতে হয় তা হল উত্তম-সুচিত্রা জুটি। আর সেই সময় বাংলা গানে হেমন্ত-সন্ধ্যা জুটি ছিল জনপ্রিয়তার শীর্ষে। বিশেষ করে উত্তম-সুচিত্রা জুটির সঙ্গীতের পরিপূরক ছিল হেমন্ত-সন্ধ্যা জুটি। ‘অগ্নিপরীক্ষা’ ছবিতে প্রথম সুচিত্রার লিপে গান করেছিলেন তিনি। আর ‘সপ্তপদী’ সিনেমার সেই অমর গান ‘এই পথ যদি না শেষ হয়’ মানুষের মণিকোঠায় চির ভাস্বর। এরকম অসংখ্য অসাধারণ গান গেয়েছেন মহানায়িকার লিপে।
দীর্ঘ্য সংগীত জীবনে অসংখ্য গান গেয়েছেন তিনি। যেমন আধুনিক গান গেয়েছেন, তেমনি গেয়েছেন রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি, লোকগীতি। পাশাপাশি গেয়েছেন খেয়াল, ভজন, ঠুংরি, কীর্তন, গজল ভাটিয়ালি প্রভৃতি। বাংলা ছাড়া আরও অনেক ভাষায়ও তিনি গান করেছেন। যা গেয়েছেন তাতেই মুগ্ধ করেছেন শ্রোতাদের। তার জনপ্রিয় গানগুলির মধ্যে রয়েছে ‘মধুমালতী ডাকে আয়’, ‘তীর বেঁধা পাখি আর গাইবে না গান’, ‘চম্পা চামেলী গোলাপের বাগে’, ‘এসো মা লক্ষ্মী বসো ঘরে’, ‘না হয় আরেকটু রহিলে পাশে’, ‘আর ডেকো না আমায়’, ‘কে তুমি আমারে ডাকো’, ‘তুমি না হয় রহিতে কাছে’, ‘কি মিস্টি দেখ মিস্টি’, ‘গানে মোর কোন ইন্দ্রধনু’, ‘ঘুম ঘুম চাঁদ’, ‘এ গানে প্রজাপতি পাতায় পাতায় রঙ ছড়ায়’ ইত্যাদি।
১৯৬০-এ তিনি বিয়ে করেন কবি শ্যামগুপ্তকে। তাদের একমাত্র সন্তান মৌনী সেনগুপ্ত। তার সঙ্গীত জীবনে স্বামীর অবদান অনেক। সংসার জীবনের অনেক দায় দায়িত্ব তার স্বামী নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছিলেন। ফলে খোলা মনে গান চালিয়ে যেতে পেরেছেন তিনি। শ্যামল গুপ্তের লেখা অনেক গান করেছেন তিনি।
শুধু একজন গায়িকা নন, একজন ভালো দরদী মনের মানুষ ছিলেন তিনি। ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। বহু বাংলাদেশি প্রাণ বাঁচাতে সীমানা পেরিয়ে ভারতে এসে আশ্রয় নেয়। সেই সব শরণার্থীদের দূর্দশা দেখে হূদয় কেঁদে ওঠে সন্ধ্যার। তাদের সাহায্য করার জন্য তিনি যোগ দেন গণ আন্দালনে। গান গেয়ে তাদের জন্য অর্থ তুলতে লাগলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য গানের মাধ্যমে সচেতনতা প্রচার করেন, বিপ্লবীদের উদ্বুদ্ধ করেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র স্থাপনে সমর দাসকে সাহায্য করেছেন। পাকিস্তান কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তি উপলক্ষ্যে গাইলেন ‘বঙ্গবন্ধু তুমি ফিরে এলে’। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন তিনি।
সঙ্গীতের জন্য বেশকিছু সম্মাননাও খেতাব পেয়েছেন তিনি। ১৯৭১ সালে ‘নিশিপদ্ম’ ছবিতে গান করে শ্রেষ্ঠ গায়িকা হিসেবে পেয়েছেন জাতীয় পুরস্কার। ২০১১ সালে পশিচ্মবঙ্গ সরকার তাকে ‘বঙ্গবিভূষণ’ খেতাব দিয়ে সম্মানিত করে। পেয়েছেন ‘গীতশ্রী’ খেতাব। ১৯৯৯-এ লইফ টাইম অ্যাচিভমেন্টের জন্য পেয়েছেন ‘ভারত নির্মাণ পুরস্কার’। ২০২২ সালে মৃত্যুর কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে ‘পদ্মশ্রী’ খেতাব দিতে চায়। কিন্তু অভিমানী, অপমানিত সন্ধ্যা সেই সম্মান নিতে অস্বীকার করেন। এতদিন ধরে গান গাইছেন তিনি। মানুষকে তার সুরের জাদুতে মুগ্ধ করেছেন। এতদিন কেন্দ্রীয় সরকার এই সম্মান দেওয়ার কথা ভাবেনি। এই ছিল তাঁর ক্ষোভ, অভিমান। আর যেভাবে তাকে সম্মাননা নেওয়ার ব্যাপারে সম্মতি জানতে চাওয়া হয়েছিল তাতে তিনি অপমানিত বোধ করেছিলেন। যে অভিমান ঝরে পড়ে তার গলায়, ‘এভাবে কেউ পদ্মশ্রী দেয়? এরা জানে না আমি কে? নব্বই বছরে আমায় শেষে পদ্মশ্রী নিতে হবে? আর এই ফোন করে বললেই চলে যাব আমি?’ তাই সম্মান ফিরিয়ে দেন তিনি। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে যে গান তিনি শ্রোতাদের উপহার দিয়েছেন, তাতে করে মানুষের মনের মণিকোঠায় থেকে যাবে তার সুর, থেকে যাবেন তিনি। এই তাঁর প্রাপ্তি, এই তাঁর বড়ো পুরস্কার। এটাই তাঁর অহংকার। তার কথায় ‘আমার পদ্মশ্রীর কোনও দরকার নেই। শ্রোতারাই আমার সব।’
২০২২-এর ১৫ ফেব্রুয়ারি ইহলোক ছেড়ে পরলোকে পাড়ি দেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। গান স্যালুটে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়। তাঁর মৃত্যুতেও একটি অভিনব ব্যাপার দেখা যায়। শ্রাদ্ধ থেকে শুরু করে সমস্ত কাজ সম্পন্ন করেন মহিলা পুরোহিতরা।
শেষ করার আগে ফিরে আসি শুরুর কথায়। জীবনের নটি দশক অতিক্রম করে থেমে গেছেন তিনি। থেমে গেছে তার পথচলা। কিন্তু সত্যিই কি পথচলা শেষ হয়েছে তার? সময়ের নিয়মে পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে তার নশ্বর শরীর কিন্তু যে অজশ্র কালজয়ী গান তিনি গেয়েছেন, তার অপূর্ব সুর মানুষের মনে গাঁথা হয়ে আছে। সেই অমর সুরের প্রবাহ আগামীর পথ ধরে এগিয়ে যাবে অনেক অনেক পথ। এইভাবে জীবন থেকে হারিয়ে গিয়েও ভীষণভাবে রয়ে যাবেন তিনি জীবনের স্রোতধারায়। আমাদের ভালোবাসার সুর ধারায় এগিয়ে চলবে তাঁর সুরের জীবন। মৃত্যুর পৃথিবীতে সুরের অমরত্ব নিয়ে এগিয়ে চলবেন তিনি অন্তহীন পথে, অনন্তের দিকে।
।।কলমে : সৌরভকুমার ভূঞ্যা।।