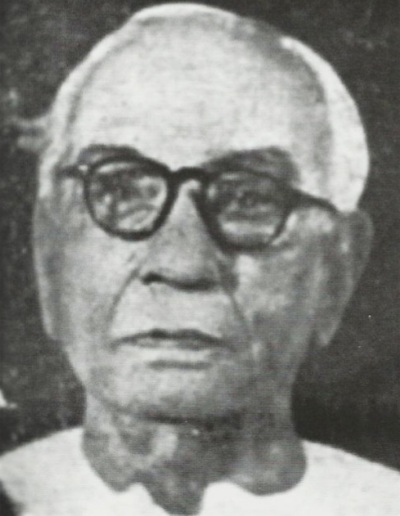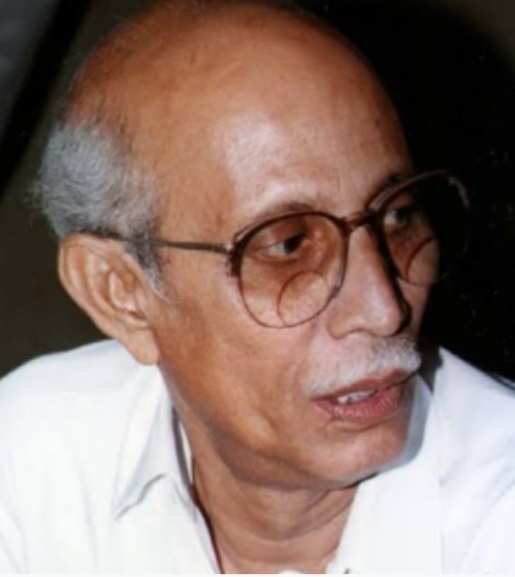গৌরী ঘোষ (বিবাহের পূর্বে গৌরী মজুমদার) (৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৩৮ – ২৬ আগস্ট ২০২১) ছিলেন একজন খ্যাতনামা ভারতীয় বাঙালি আবৃত্তিকার তথা বাচিক শিল্পী। তিনি ও তার স্বামী পার্থ ঘোষ বাংলা আবৃত্তি জগতে ছিলেন অন্যতম জুটি। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধের সময় অসামান্য কাজের জন্য বাংলাদেশ সরকারের “মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মান” ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের “কাজী সব্যসাচী সম্মান” লাভ করেন।
জন্ম ও শিক্ষা জীবন—
গৌরী মজুমদারের জন্ম ১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দের ৩০ সেপ্টেম্বর ব্রিটিশ ভারতের অধুনা বিহার রাজ্যের কাটিহারে। সেদিন ছিল শারদীয়া দুর্গাপূজার মহাষষ্ঠী, তাই নাম রাখা হয়েছিল গৌরী। পিতা অমূল্যকুমার মজুমদার ছিলেন ভারতীয় রেলের কর্মচারী। তার মা ছিলেন রবীন্দ্র কবিতা অনুরাগী। তাদের আদি নিবাস ছিল অধুনা পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার চোপা গ্রামে। তার মেজদা ছিলেন প্রখ্যাত গায়ক ও চলচ্চিত্র অভিনেতা রবীন মজুমদার। পিতার বদলির কারণে তাকে বিভিন্ন স্থানে ঘুরতে হয়। প্রাথমিক পাঠ শেষে কিছুদিন কলকাতায় অবস্থানের সময় মুরলীধর গার্লস হাইস্কুলে পড়াশোনা করেন। সেখানে তার প্রিয় বান্ধবী ছিলেন ঋতু গুহ। পরে আবার কাটিহারে ফিরে গেলে বাড়িতেই পড়াশোনা করেন এবং প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করেন। গৌরীর জীবনে তার মেজদা রবীন মজুমদারের প্রভাব ছিল অপরিসীম। তার সহযোগিতায় ও প্রশ্রয়ে তিনি কলকাতায় থেকে স্নাতক হন, এম.এও পাশ করেন।
কর্মজীবন—
এম.এ পাশের পর কিছুদিন শিক্ষকতাও করেন। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে উপস্থাপিকা-ঘোষিকা হিসাবে যোগ দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। প্রায় তিন দশকের বেশী সময় ধরে কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত আকাশবাণীর অনেক অনুষ্ঠানে গৌরীর কণ্ঠে সুরম্য উপস্থাপনা শুনেছেন বাংলার শ্রোতারা। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিবাহ করেন আর এক সুস্নাত ব্যক্তিত্বের আবৃত্তিকার পার্থ ঘোষকে। বাংলার আবৃত্তি জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্রজুটি তথা গৌরী ঘোষ ও পার্থ ঘোষ দম্পতি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। তারা আবৃত্তি ও শ্রুতিনাটককে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দেন। তাঁদের যৌথ শ্রুতি নাটক ‘কর্ণকুন্তি সংবাদ’ জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছে কিংবদন্তি হয়ে ওঠে সেসময়। আকাশবাণীতে দীর্ঘদিন কাজ করা ছাড়াও মঞ্চেও উপস্থাপনা করেছেন তারা। বাংলা কবিতা নিয়ে তাদের একাধিক সিডি-ক্যাসেট রয়েছে। এরমধ্যে ‘এই তো জীবন’সহ বেশ কয়েকটি জনপ্রিয়।
তিনি পশ্চিমবঙ্গ কবিতা আকাদেমির সদস্যও ছিলেন।
মূলত আবৃত্তিকার বা বাচিক শিল্পী হিসাবে পরিচিতি থাকলেও তিনি বাংলা চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিপ্রাপ্ত ছায়াছবি ঋতুপর্ণ ঘোষের অসুখ (চলচ্চিত্র) রোহিনীর মা’র ভূমিকায় অভিনয় করেন।
সাংস্কৃতিক জগতের ব্যক্তি হয়েও ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে বহু অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন গৌরী ঘোষ। স্বাধীনতার পক্ষে জনমত গঠনের পাশাপাশি শরণার্থীদের ত্রাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন। তার স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন “উপমা” মাধ্যমে দুঃস্থদের সাহায্যও করেছেন বিভিন্ন সময়ে।
মৃত্যু—
বেশ কিছুদিন গৌরী ঘোষ বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছিলেন। ২০২১ খ্রিস্টাব্দে আগস্ট মাসের মাঝামাঝি সময়ে তার মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয় এবং তখন থেকে অবস্থার অবনতি হতে থাকে। সপ্তাহখানেকের বেশী সময়ে তিনি কলকাতার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইন্টারন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব কার্ডিয়াক সাইন্সে ভর্তি ছিলেন। অবশেষে ২৬ আগস্ট তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।
পুরস্কার—
মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তার অসামান্য অবদানের জন্য বাংলাদেশ সরকার ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে ‘মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সম্মান’ প্রদান করে। তার অনবদ্য আবৃত্তি বাংলার শ্রোতাদের হৃদয়ে যে অনুভূতি জাগ্রত করে তারই স্বীকৃতিস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে “কাজী সব্যসাচী পুরস্কার” প্রদান করে।
গৌরী ঘোষ ও পার্থ ঘোষের জীবন আধারিত তথ্যচিত্র – এমন তরণী বাওয়া মুক্তি পায় গৌরী ঘোষের জন্ম দিন উপলক্ষ করে ২০২১ খ্রিস্টাব্দের ৩০ সেপ্টেম্বর কলকাতার মধুসূদন মঞ্চে।
।।তথ্য : সংগৃহীত উইকিপিডিয়া।।