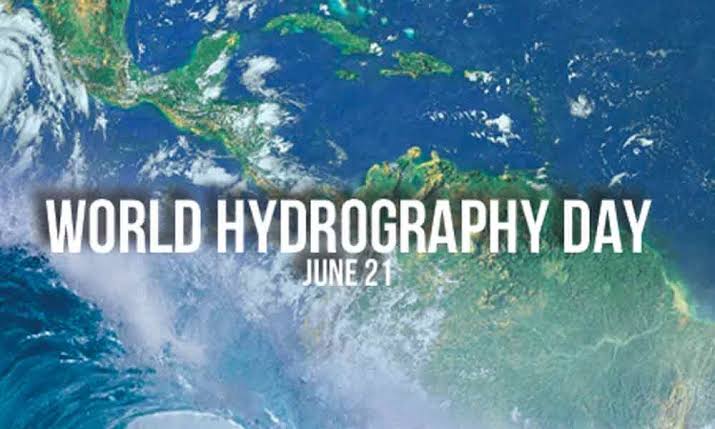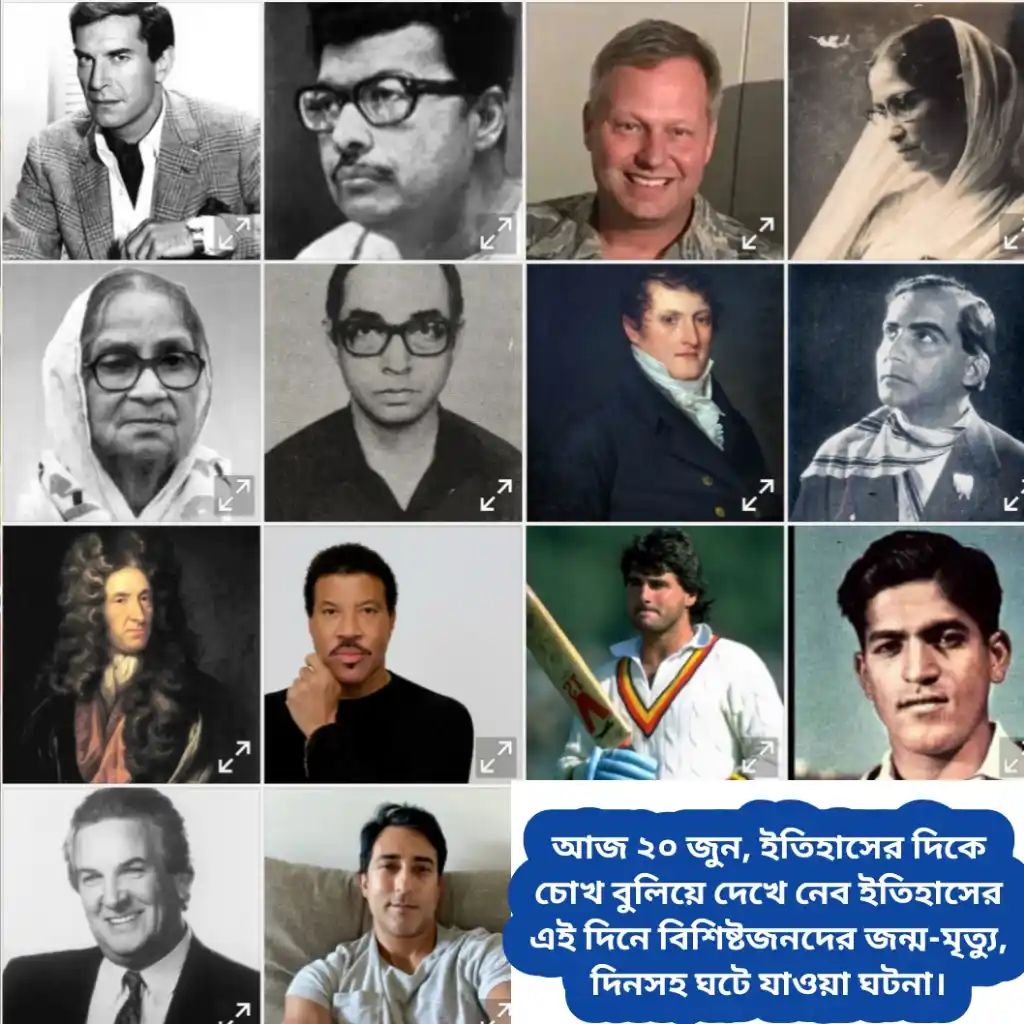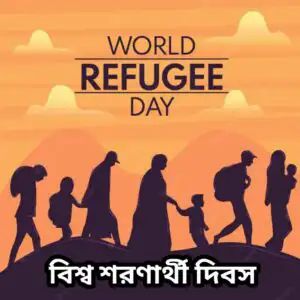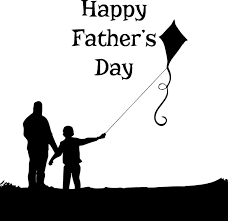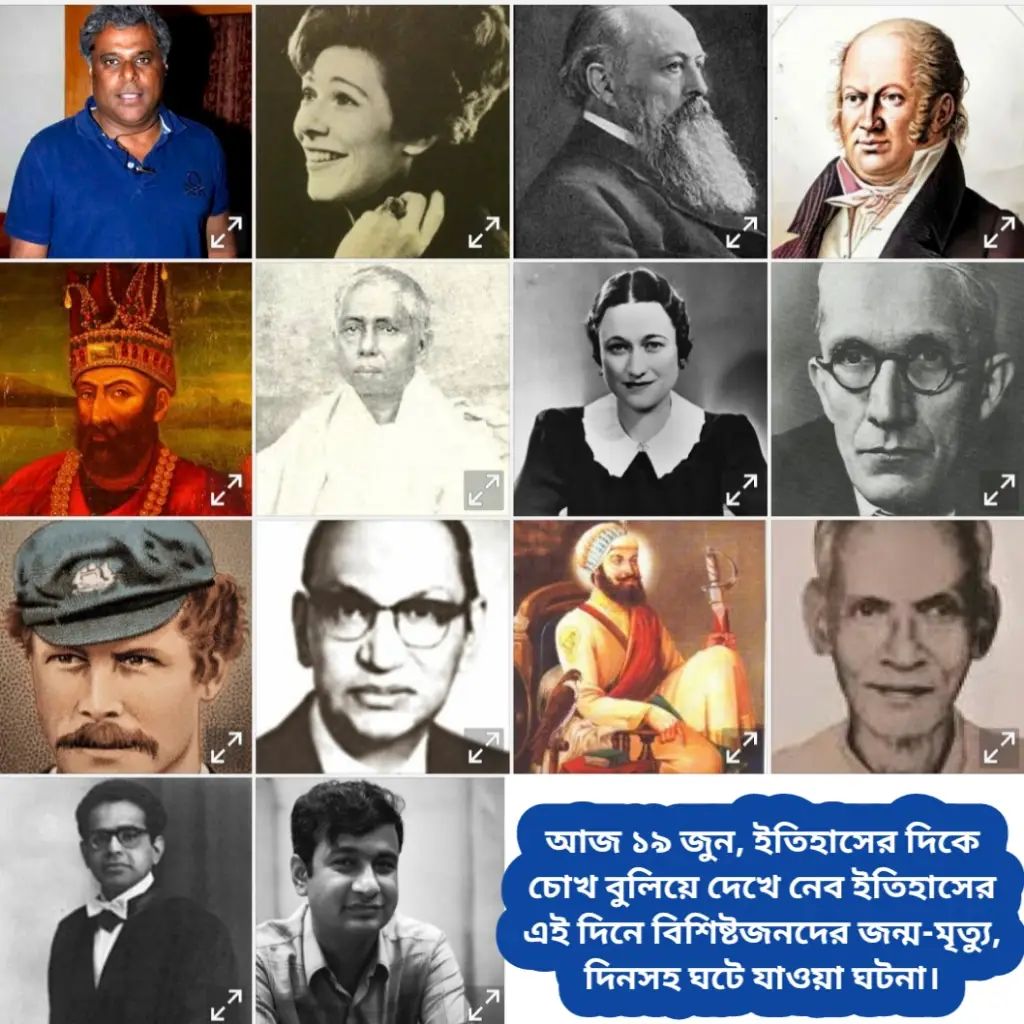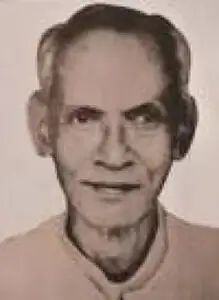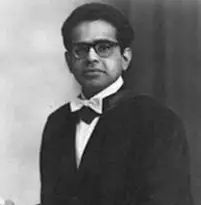বিশ্ব সঙ্গীত দিবস ২০২৫: ‘ফেটে দে লা মিউজিক’ নামেও পরিচিত, বিশ্ব সঙ্গীত দিবসের বিশেষ উপলক্ষ সঙ্গীত এবং এর সার্বজনীন ভাষা প্রচারের জন্য প্রতি বছর ২১ জুন পালিত হয়। বিশ্ব সঙ্গীত দিবসে, লোকেদের তাদের আশেপাশের বা পার্কের মতো পাবলিক স্পেসে বাইরে গান বাজানোর জন্য আহ্বান জানানো হয়।
এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হল সঙ্গীত প্রচার করা এবং অপেশাদার এবং পেশাদার সঙ্গীতজ্ঞদেরকে রাস্তায় পরিবেশন করতে উত্সাহিত করা হয়, ‘ফাইটস দে লা মিউজিক’ স্লোগানের অধীনে।
“বিশ্ব সঙ্গীত দিবস ২০২৫ ইতিহাস—-
বিশ্ব সঙ্গীত দিবস ১৯৮২ সালে ফ্রান্সে একটি সমৃদ্ধ পটভূমি এবং ইতিহাসের সাথে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জ্যাক ল্যাং, তৎকালীন ফরাসি সংস্কৃতি মন্ত্রী, সুরকার মরিস ফ্লুরেট এবং একজন রেডিও প্রযোজক যিনি একজন সঙ্গীত সাংবাদিক হিসাবে দ্বিগুণ হয়েছিলেন, তিনি সংগীতের জন্য উত্সর্গীকৃত একটি দিন প্রতিষ্ঠার ধারণাটি প্রস্তাব করেছিলেন। ২১শে জুন, গ্রীষ্মের অয়নকাল, গায়ক এবং সঙ্গীতজ্ঞরা সঙ্গীতের রূপান্তরকারী শক্তিকে সম্মান জানাতে পাবলিক স্পেসে জড়ো হয়।”
একটি সাধারণ ভাষা হিসাবে সঙ্গীত ব্যবহার করে, বিশ্ব সঙ্গীত দিবস বাদ্যযন্ত্রের বৈচিত্র্যকে এগিয়ে নিতে এবং সম্প্রদায়ের বোধ গড়ে তুলতে চায়। প্যারিস ২১ জুন, ১৯৮২ তারিখে উদ্বোধনী বিশ্ব সঙ্গীত দিবস পালন করে। উৎসবটি একটি দুর্দান্ত সাফল্য ছিল, যেখানে এক হাজারেরও বেশি সংগীতশিল্পী এবং গায়ক পার্কে এবং রাস্তায় পরিবেশন করেছিলেন। তারপর থেকে, মানুষ এই উপলক্ষটি সারা বিশ্বে উদযাপন করেছে।
তাৎপর্য্য———
বিশ্ব সঙ্গীত দিবসের উদ্দেশ্য হল সঙ্গীতকে এমন একটি শিল্পের স্তরে উন্নীত করা যা সব বয়সের মানুষের কাছে আরও সহজলভ্য। একটি উন্মুক্ত পরিবেশ তৈরি করা, লোকেদের বিভিন্ন ধরণের সংগীত শুনতে উত্সাহিত করা এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য শিল্পকে আলিঙ্গন করা সবই সম্মানিত। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হল সঙ্গীত। প্রত্যেকে তাদের দৈনন্দিন কাজগুলি করতে যাওয়ার সময় গান শুনতে উপভোগ করে, তা ভ্রমণ করা, বাড়ির কাজ শেষ করা বা কেবল রান্না করা। সঙ্গীত সত্যিই আমাদের সেরা বন্ধু।
বিশ্ব সঙ্গীত দিবস ২০২৫ থিম—-
এই বছরের দিবসের প্রতিপাদ্য এখনও ঘোষণা করা হয়নি। যারা সঙ্গীত শুনতে পছন্দ করেন তারা সঙ্গীত এবং গান শুনে এই উপলক্ষটি উদযাপন করতে পারেন। এটি উল্লেখ করা উচিত যে ফ্রান্সের সংস্কৃতি মন্ত্রী জ্যাক ল্যাং এবং সঙ্গীত রচয়িতা মরিস ফ্লুর প্রথম সঙ্গীত উদযাপনের আয়োজনকারীদের মধ্যে ছিলেন। ১৯৮২ সালের উদযাপনের পর, বিশ্ব সঙ্গীত দিবস এখন বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশে পালিত হয় এবং এটি একটি বিশ্বব্যাপী ঘটনা হয়ে উঠেছে। ভারত, ইতালি, অস্ট্রেলিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, চীন এবং মালয়েশিয়ায় সঙ্গীত দিবস পালিত হয়। অপেশাদার সঙ্গীতজ্ঞ এবং প্রবীণরা সঙ্গীত পরিবেশন করতে এবং বিভিন্ন সঙ্গীত অনুষ্ঠানে অংশ নিতে রাস্তায় নেমে আসেন। প্যারিসের রাস্তাগুলি সঙ্গীতের সুরে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে এবং সঙ্গীতপ্রেমীরা এতে দোল খায়। ফ্রান্সের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সঙ্গীতপ্রেমীরা ফেটে দে লা মিউজিকের জন্য প্যারিসে ভিড় জমান, যেখানে উৎসব, ভোজ, কুচকাওয়াজ এবং মেলা অন্তর্ভুক্ত থাকে।
বিশ্ব সঙ্গীত দিবস ২০২৫ উদ্ধৃতি—–
(১) সঙ্গীত একটি নৈতিক আইন। এটি মহাবিশ্বে আত্মা, মনকে ডানা, কল্পনার ফ্লাইট, এবং জীবন এবং সবকিছুর জন্য আকর্ষণ এবং আনন্দ দেয়।
(২) যদি সঙ্গীত আপনাকে জাগিয়ে তোলে, আপনাকে ভাবতে বাধ্য করে, আপনাকে সুস্থ করে তোলে… তাহলে, আমি অনুমান করি যে সঙ্গীত কাজ করছে।
(৩) সঙ্গীত মানবজাতির সর্বজনীন ভাষা।
।। তথ্য : সংগৃহীত উইকিপিডিয়া ও বিভিন্ন ওয়েবসাইট।।