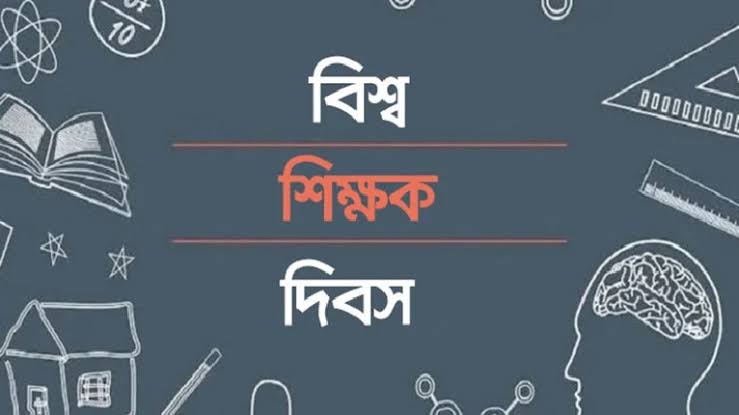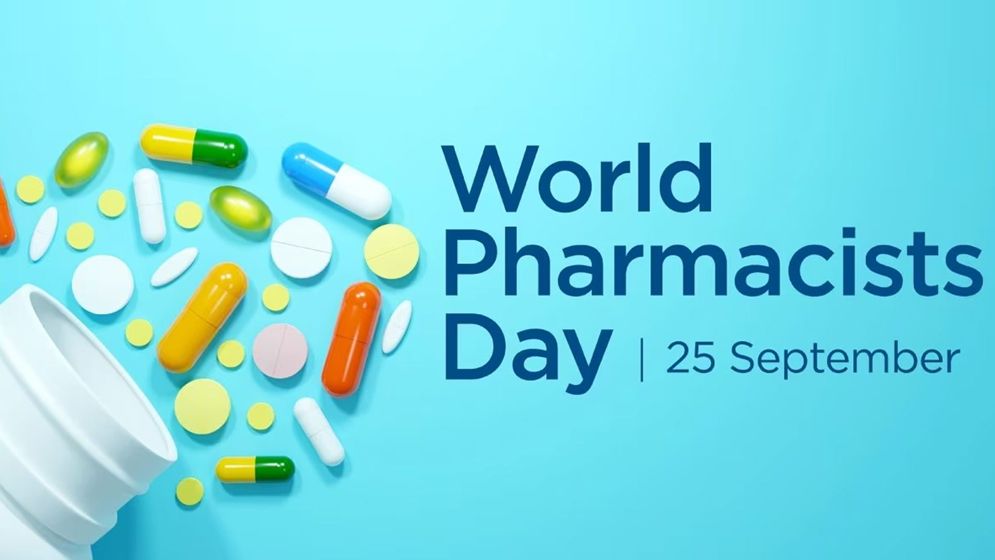ॐ সর্বমঙ্গল- মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থ -সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোহস্তু তে।।
শ্রীশ্রী চণ্ডী এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুসারে ও রামায়ণ অনুযায়ী ত্রেতা যুগে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র অকালে দেবীকে আরাধনা করেছিলেন লঙ্কা জয় করে সীতাকে উদ্ধারের জন্য। কিন্তু, আসল দূর্গা পূজা হলো বসন্তে, সেটাকে বাসন্তি পূজা বলা হয়। শ্রীরামচন্দ্র অকালে-অসময়ে পূজা করেছিলেন বলে এই শরতের পূজাকে দেবির অকাল-বোধন বলা হয়। বোধন অর্থ জাগরণ। তাই মহালয়ার পর দেবীপক্ষের (শুক্লপক্ষের) প্রতিপদে ঘট বসিয়ে শারদীয়া দুর্গা পুজার সূচনা করা হয়। প্রসঙ্গতঃ শ্রাবণ থেকে পৌষ ছয় মাস দক্ষিণায়ন, দক্ষিণায়ন দেবতাদের ঘুমের কাল। তাই বোধন অবশ্যই প্রয়োজন হয়। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কা বিজয়ের আগে এমনই অকাল-বোধন করেছিলেন। তবে সাধারণত আমরা ষষ্ঠি থেকে পূজার প্রধান কার্যক্রম শুরু হতে দেখি যাকে বলা হয় ষষ্ঠাদিকল্পরম্ভা। কিছু প্রাচীন বনেদী বাড়ি এবং কিছু মঠ মন্দিরে প্রতিপদ কল্পরম্ভা থেকে ও পুজো হয়। যদিও প্রতিপদ কল্পরম্ভা থেকে শুরু পুজোতেও আনুষ্ঠানিক মূল কার্যক্রম শুরু হয় ষষ্ঠি থেকেই এবং সপ্তমী থেকে বিগ্রহতে। প্রতিপদ থেকে শুধু ঘটে পূজো ও চণ্ডী পাঠ চলে।
সাধারণত আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠ থেকে দশম দিন পর্যন্ত শারদীয়া দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই পাঁচটি দিন যথাক্রমে “দুর্গাষষ্ঠী”, “দুর্গাসপ্তমী”, “মহাষ্টমী”, “মহানবমী” ও “বিজয়াদশমী” নামে পরিচিত। আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষটিকে বলা হয় “দেবীপক্ষ”। শ্রীশ্রী চণ্ডী এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণ অনুসারে মেধস মুনির আশ্রমেই পৃথিবীর প্রথম দুর্গাপুজো আয়োজিত হয়েছিল। এটি পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর মহকুমার কাঁকসার গড় জঙ্গলে অবস্থিত। দুর্গাপুর থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরত্বে রয়েছে গড় জঙ্গল। জঙ্গলের মধ্যে ২-৩ কিলোমিটার গেলেই পাওয়া যাবে মেধসাশ্রম। পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরের নিকটবর্তী গড় জঙ্গলে মেধসাশ্রমে ভূভারতের প্রথম দুর্গাপূজা হয়। এখানেই রাজা সুরথ বাংলা তথা মর্তে প্রথম দুর্গাপূজা করেছিলেন। কাঁকসার গড় জঙ্গলের গভীর অরণ্যের মেধাশ্রম বা গড়চণ্ডী ধামে কোনও এক সময়ে রাজা সুরথ ও সমাধি বৈশ্য পুজো শুরু করেন। বসন্তকালে সূচনা হয় পুজোর৷ বসন্তের নবরাত্রির পূজা বাসন্তিক বা বসন্তকালীন দুর্গাপূজা নামে পরিচিত। তারপর থেকেই বাংলা তথা ভূভারতে দুর্গাপুজোর প্রচলন হয়।
মহর্ষি মেধস মুনি বলিলেন, “মহামায়া পরমা জননী অর্থাৎ আদিমাতা৷ যখন এই জগৎ ছিল না, তখন তিনি ছিলেন। যখন সূর্য্য ছিল না, চন্দ্র ছিল না, তারা নক্ষত্র এই পৃথিবী কিছুই ছিল না, তখন তিনি ছিলেন। তাঁহা হইতেই এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে৷ তিনি এই জগৎকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া তাঁহার নাম মহামায়া। জগৎকে তিনি সৃষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই তিনি জগৎকে ধরিয়া আছেন, এই জন্য তাঁহার আর এক নাম জগদ্ধাত্রী। তিনি ধারণ করিয়া না থাকিলে উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই এ জগতের- লয় হইয়া যাইত।শক্তিরূপা সনাতনী আপনার বিশ্ব বিমোহিনী মায়া দ্বারা আপনাকে আচ্ছাদিত করিয়া নানারূপে আমাদের মধ্যে লীলা করিতে আসেন। কখনও তিনি পিতা মাতার কাছে নন্দিনী, ভ্রাতার কাছে ভগিনী, পতির কাছে জায়া, পুত্র কন্যার কাছে জননী। কখনও তিনি দীনের কাছে দয়া; তৃষিতের কাছে জল, রোগীর কাছে সেবা, ক্ষুধিতের কাছে ফল। কখন কত মূর্তিতে যে মা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হন তাহা আর কি বলিব ? তাঁহার গুণ বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারে, এমন শক্তি এ জগতে কার আছে ? তিনি আসিলেই জীবের সকল দুর্গতির অবসান হয়। এইজন্য তাঁহার আর এক নাম দুর্গা। দুর্গতিনাশিনী শ্রীদুর্গাই ভুবনমোহিনী ত্রিজগৎ প্রসবিনী আদ্যাশক্তি মহামায়া।
দুর্গাপূজা বা দুর্গোৎসব হল দেবী দুর্গার পূজাকে কেন্দ্র করে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রচলিত একটি প্রধান উৎসব। বর্তমানে এটি সারা বিশ্বে পালিত হয়, তবে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ওড়িশা, বিহার, ত্রিপুরা, ঝাড়খণ্ড, উত্তর প্রদেশ (পূর্বাঞ্চল) এবং বাংলাদেশে ঐতিহ্যগত বিশেষভাবে উদযাপিত হয়। এটি বাংলা বর্ষপঞ্জির আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গাপূজা মূলত দশ দিনের উৎসব, যার মধ্যে শেষ পাঁচটি দিন সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। আশ্বিনের নবরাত্রির পূজা শারদীয় পূজা এবং বসন্তের নবরাত্রির পূজা বাসন্তিক বা বসন্তকালীন দুর্গাপূজা নামে পরিচিত।
২০২১ সালের ডিসেম্বরে কলকাতার দুর্গাপূজা ইউনেস্কোর (UNESCO) অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় যুক্ত করা হয়। কলকাতা শহর এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসবকে (UNESCO) আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিয়েছে।
দুর্গাপুজোর সপ্তমীতে মাদুর্গার আগমন আর গমন দশমীতে। এই দুই দিন সপ্তাহের কোন বারে পড়ছে, তার উপরই নির্ভর করে দেবী কিসে আসবেন বা কিসে যাবেন। শাস্ত্রে বলা হয়েছে “রবৌ চন্দ্রে গজারূঢ়া,ঘোটকে শনি ভৌময়োঃ, গুরৌ শুক্রে চ দোলায়াং নৌকায়াং বুধ বাসরে।।” শুরুতেই বলা হচ্ছে, ‘রবৌ চন্দ্রে গজারূঢ়া’ অর্থাৎ, সপ্তমী যদি রবিবার বা সোমবার হয়, তাহলে দুর্গার আগমন হবে গজে বা হাতিতে। একই ভাবে, দশমীও রবি বা সোমে পড়লে দুর্গার গমন বা ফেরা হবে গজে। এরপর বলা হচ্ছে, ‘ঘোটকে শনি ভৌময়োঃ’ অর্থাৎ শনি বা মঙ্গলবার সপ্তমী পড়লে দেবীর আগমন হবে ঘোটকে বা ঘোড়ায়। দশমীও শনি বা মঙ্গলে পড়লে ফিরবেন ঘোড়ায়। তারপর রয়েছে, ‘গুরৌ শুক্রে চ দোলায়াং’ অর্থাৎ বৃহস্পতি বা শুক্রবারে সপ্তমী পড়লে দেবী দোলায় আসবেন আর দশমী পড়লে দেবী দোলায় ফিরবেন। সব শেষে বলা হচ্ছে, ‘নৌকায়াং বুধবাসরে’ অর্থাৎ, বুধবার সপ্তমী পড়লে দেবীর নৌকায় আগমন এবং দশমী পড়লে নৌকায় গমন। এই হল সপ্তাহের সাত দিনের নিয়ম। যেমন, এই বছর দুর্গাপুজোর সপ্তমী পড়েছে বৃহস্পতি, অর্থাৎ হিসেব মতো এ বার দেবীর আগমন দোলায়। আবার, দশমী পড়েছে শনিবার, ফলে দেবীর গমন হবে ঘোটকে।
দুর্গাপুজোর সন্ধিপূজা মহাঅষ্টমীর শেষদন্ড ও মহানবমীর প্রথমদণ্ডে অনুষ্ঠিত খুব গুরুত্বপূর্ণ। এত গুরুত্বপূর্ণ হবার কারণ পুরাণে পাওয়া যায়। অষ্টমীতিথির শেষ ২৪মিনিট ও নবমীতিথির প্রথম ২৪মিনিট মিলিয়ে মোট ৪৮মিনিট সময়ের যে মহাসন্ধিক্ষণ সেই সময়ে সন্ধিপূজা করা হয়। বলা হয়ে থাকে ঠিক এই সময়েই দেবী দুর্গা চন্ড ও মুন্ড নামে দুই ভয়ঙ্কর অসুরের নিধন করেছিলেন। এই ঘটনাটি মনে রাখার জন্যই প্রতি বছর অষ্টমী এবং নবমীর সন্ধিক্ষণে এই সন্ধিপূজা করা হয়। দুর্গা পুজোর এই মহাসন্ধিক্ষনে মহাশক্তিশালী “চামুন্ডা কালিকা” দেবীরই আরাধনা করা হয়। সন্ধিপূজায় ১০৮টি পদ্ম এবং ১০৮টি প্রদীপ জ্বালিয়ে সাজিয়ে দেওয়ার নিয়মটি চিরাচরিত, এর কোনো অন্যথা করা হয় না। বলা হয় পদ্ম হল ভক্তির প্রতীক এবং প্রদীপ জ্বালানো জ্ঞানের প্রতীক। আর এই যে চণ্ড এবং মুণ্ড হল যথাক্রমে মানুষের মনের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি এর প্রতীক। প্রবৃত্তি অর্থে ভোগ এবং নিবৃত্তি অর্থে ত্যাগ। মোক্ষলাভের জন্য এই দুইকেই বধ করার মাধ্যমে দেবী চণ্ডীর পূজা করা হয় এবং তা করা হয় এই সন্ধিপূজায়।
দুর্গাপুজোর যেটি বহুল প্রচলিত রূপ- তা হল ষষ্ঠাদি কল্প। এই নিয়ম অনুযায়ী মহানবমীর পুজা অন্তিম পুজা। সংকল্পে ‘মহানবমী যাবৎ’ এর সংকল্প গ্রহণ করা হয়। চণ্ডিপাঠ, দুর্গানাম জপ মহানবমী অবধি অনুষ্ঠানের সংকল্প নেওয়া হয় বোধনের দিন। সেই মতো হোমের মাধ্যমে মহানবমীতে দেবীর সংকল্পিত মহাপুজার ইতি ঘটে। এরপর দশমী পুজা শুধুমাত্র দেবী বিদায়ের আচরিত সংক্ষিপ্ত পুজা। মহাষষ্ঠী, মহাসপ্তমী, মহাঅষ্টমী, মহানবমী এবং বিজয়া দশমী হিসেবে পরিচিত। তবে বিজয়া দশমীর দিন চারিদিকে বাজে বিষাদের সুর। কারণ উমার ফিরে যাওয়ার পালা। বিজয়া দশমী দুর্গাপুজোর উৎসবের শেষ দিন। প্রতিমাগুলি বরণ করে মহিলারা ‘সিঁদুর খেলা’-এ মেতে ওঠেন। এরপর জলাশয়ে বিসর্জন দেওয়ার হয় প্রতিমাগুলি। ঘট বিসর্জনের অর্থ, পুজো সমাপ্তি। বিসর্জনের সময় লম্বা শোভাযাত্রা বের করে। যেখানে নাচে-গানে, হাসি-কান্না মুখে সকলে বিদায় জানান উমাকে। এদিন বরণ, সিঁদুর খেলা, বিসর্জনের মাধ্যমে দুর্গাপুজোর ও বিজয়া উৎসবের সমাপ্তি হয়।
আবার বারো ইয়ার বা বন্ধু মিলে ওই পুজো ‘বারোইয়ারি’ বা ‘বারোয়ারি’ পূজা নামে খ্যাত হয়। সেই থেকেই আজকের বারোয়ারি পুজোর বিবর্তন। সেদিনের সেই ‘বারোয়ারি’ কথাটি ধীরে ধীরে বর্তমানে আপামর বাঙালির ‘সর্বজনীন’ কিংবা ‘সার্বজনীন’ এ রূপান্তরিত। সার্বজনীন পূজা ছাড়া ও বর্তমানে রাজবাড়ী, জমিদার বাড়ি, কিছু প্রাচীন বনেদী বাড়ি এবং কিছু মঠ মন্দিরে এছাড়া ও বিভিন্ন আশ্রম, মঠ ও মিশনে সন্ন্যাসীরা দুর্গাপূজার আয়োজন করেন। কিন্তু, *বাংলায় অসুরদের দ্বারা মা অভয়ার মর্মান্তিক পরিণতির জন্য এই বছর সব যেন কেমন বিষণ্ণ, মলিন, কোথাও যেন প্রাণের ছোঁয়া নেই।* আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আর মা দূর্গার মর্ত্যে অবতরণ সকল মর্ত্যবাসীর জন্য সুসংবাদ ও আনন্দ নিয়ে আসুক, অসুরদের বধ হোক, জয় মা দুর্গা-জয় মা দূর্গা-জয় মা দূর্গা দূর্গতিনাশিনী… জগৎ জননী মাদূর্গা তোমার আশির্বাদ সকলের মস্তকে বর্ষিত হোক। জগৎ গুরু ভগবান স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের শুভ ও মঙ্গলময় আশির্বাদ আপনাদের সকলের শিরে বর্ষিত হোক, পিতা-মাতার আশির্বাদ সকলের শিরে বর্ষিত হোক, এই প্রার্থনা করি.!
ওঁ গুরু কৃপা হি কেবলম্ ।l
স্বামী আত্মভোলানন্দ (পরিব্রাজক)